বাতাসের বীজতলা
ভূমিকা-
কেবলি ভেঙে টুকরো হয়ে যায় মৃত্যু, অপরূপা মেয়ে!
বাতাসের ঘরে জন্মায় অদ্ভুত; যৌন তাড়িত অব্যয়ে…
বাতাসের বীজতলা
ঠোঁটের কারফিউ ভাঙ্গে নিঃশব্দ আঙুল
সমাজ, দেশ এবং বৈশ্বিক সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহকে কবি মনিরুল হক এমরান কবিতার শৈল্পিক ভাষায় নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কাব্য গ্রন্থে কবি প্রেম-দ্রোহ, কষ্ট-ক্ষোভ ও মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবনের চিত্র এঁকেছেন। তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট উপজীব্য। হিংসা-প্রতিহিংসা, বকধার্মিকদের ধর্মাধর্মের বাড়াবাড়ি, মানুষের প্রতি মানুষের নিষ্ঠুরতাকে প্রতিবাদ করেছেন কবিতার মাধ্যমে শব্দের দক্ষ কারিগরের হাতে। পাঠকের জন্য সুখপাঠ্য করে তুলেছেন প্রতিটি কবিতা। এই গ্রন্থে পাঠকের মনকে আনন্দে আন্দোলিত করার মত রয়েছে তাঁর তের্জারিমা ছন্দে লেখা পনেরটি তের্জারিমা কবিতা। দুই খ-ের তের্জারিমা বই প্রথম প্রকাশিত হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩ এবং ২০১৫ সালে। যা পরবর্তীতে পাঠক ও কবিদের মাঝে সমাদৃত হয় এবং অনেক নবীন কবি চর্চা করতে শুরু করেন। এবারের কবিতার বইটি খানিকটা ভিন্নভাবে, কবির নিজস্ব ছন্দের কয়েকটি কবিতা রয়েছে। আশা করি পাঠক বইটি পড়ে নির্মল আনন্দ পাবেন। -প্রকাশক
ঠোঁটের কারফিউ ভাঙ্গে নিষিদ্ধ আঙুল
শাদা কফিনে মেঘের শব্দ
মাহবুব মিত্র বিশ্বাস করেন মানুষই শিল্প; মানবতাই ধর্ম। মানুষবিহীন পৃথিবী শস্যহীন প্রান্তরের মতো। তিনি মনে করেন সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প মানুষের সৌন্দর্য। তাঁর প্রিয় বিখ্যাত দু’টি উক্তিÑ “মানুষ দেখার আনন্দে তুমি কখনো ক্লান্ত হয়ো না”, “ভুল মানুষের কাছে আমি নতজানু নই।” নীতির সাথে আপোসহীন চির প্রতিবাদী সতত ডানার মানুষ এক ক্লান্তিহীন গেয়ে যান ভালোবাসার গান, সমতার গান, মানবতার গান, সুন্দরের গান।
মাহবুব মিত্র বস্তুবাদী দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাসী। আবার ভাববাদী দর্শনও মাঝে-মধ্যে তাঁকে ভাবায়। এই দুই মতবাদের ভিতর দিয়ে পথ হাঁটছেন। তিনি বুকে ধারণ করে আছেন সৃষ্টি জগতের সকল সুন্দরের নির্যাস। সাহিত্য ও শিল্পের বাগানে শব্দ বুনে-বুনে তৈরী করছেন মানব হৃদয়ের নৈবেদ্য। এই নিবিড় সংসারে একাকি নিঃসঙ্গ পথিক এক খুঁজে পেয়েছেন জীবনের সৌন্দর্যের অবিরাম ধারাপাত। তিনি মানব হৃদয়ে খুঁজে বেড়ান সুন্দরের স্বর্গভূমি।
তিনি সর্বদা আশাবাদী একজন প্রাণবন্ত-প্রফুল্ল মানুষ। তুমুল অন্ধকারের মাঝে খুঁজে ফেরেন আলোর ফোয়ারা। মানুষ তখনই মৃত যখন তার ভিতরের আনন্দ মরে যায়। চিরন্তন সুন্দরের জন্য হাহাকার-আকাক্সক্ষা, নৈতিক মূল্যবোধের উপলব্ধি, স্বতন্ত্র বোধের-চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর ভাবনার আকাশ। তাঁর সুকুমার কোমল প্রবৃত্তি আপন আলোয় ভাস্বর, দীপ্ত-শোভান্বিত, সদা জাগ্রত।
শাদা কফিনে মেঘের শব্দ
ধুন্ধুমার
আকাশের বুকে মানুষের পা হাঁটে না, চোখ হাঁটে। দিগন্তের দিকে যেই চোখ পড়ে মন ছুটে যায় নিমিষে। এই যে চোখের সাথে মনের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র সেখানেই কবিতার বসবাস। কবিতা মানুষকে আকাশে হাঁটায়, দিগন্তে ঘুরায় আর সৌন্দর্যের আতিশয্যে বসবাস করায়। বর্তমানে বিজ্ঞানের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন, এই যে আমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল- এসবের সুন্দর ও নান্দনিক প্রতিফলন মেলে কবিতায়। সমালোচক কবি Arnold কবিতাকে বলছেন, ‘Criticism of life.’ সিডনি তাঁর ‘An Apology for Poetry’-তে কবিতাকে দেখছেন ‘A divine gift’ হিসেবে। আমরা বাঙালি। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। ভাষার জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হয়েছে। আমাদের দেশ বাংলাদেশ। দেশের জন্য লক্ষ লক্ষ জনতার প্রাণ গেছে। ভাষার জন্য, দেশের জন্য যে মানুষটি আমাদের পথ হাঁটিয়েছেন তিনি হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
কিছু বিপথগামী সেনাবাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধুর প্রাণহরণ কবি মাহবুব জন-কে গভীরভাবে আলোড়িত করে। সৃষ্টিশীল মানসপটে নতুন প্রজন্মের কবি মাহবুব জন দেশ, মাটি তথা মাতৃভূমি, সমাজ, গোষ্ঠী, চারপাশের দৃশ্যাবলী- তীক্ষè অনুভূতির এক উজ্জ্বল আলোকছটা তাঁর এ ‘ধুন্ধুমার’ কাব্যগ্রন্থটি। যেমনটি Arnold তাঁর`The Study of Poetry’ -তে বলেছেন, ‘Greatness of matter is inseparable from the greatness of manner’- পাঠক অনায়াসেই মাহবুব জন-এর ‘ধুন্ধুমার’ কাব্যগ্রন্থের সুন্দর বিষয়বস্তু এবং কাব্যিক বিন্যাসে মুগ্ধ হবেন।
ধুন্ধুমার
লাশপুরীর লাশের গল্প
ভূমিকা
লোকমান তাজ রচিত লাশপুরীর লাশের গল্প কিশোর উপযোগী রহস্যময় উপন্যাস। সমকালীন অনেক লেখক এ জাতীয় রচনা সৃষ্টিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সাইন্স ফিকশন, রম্য কথা, ভৌতিক থ্রিলিং ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রচুর লেখালেখি অব্যাহত রয়েছে। কারো কারো বেলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তাও লক্ষণীয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব লেখা অনির্দেশ্য বায়বীয় ভাব ভাবনায় সমর্পিত।
সঠিক কোনো জীবনবোধ বা আদর্শ অন্বেষার বালাই নেই। দিকভ্রান্ত কাহিনী চরিত্রের মোহমুগ্ধ ঘনঘটা একটা আবেশ ছাড়িয়ে দেয়।
এ অবস্থায় লোকমান তাজ এর লাশপুরীর লাশের গল্প নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এখানে গাছতলা গ্রামের সবিস্তার কাহিনী সাব্বির, মাহি ও মেহেক চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হয়েছে। তাছাড়া আরো কিছু শাখা কাহিনীও এখানে প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। যেখানে মীরাকে কেন্দ্র করে ছাত্রীনিবাসের এক মর্মান্তিক কাহিনী এখানে বর্ণিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র সাব্বিরই পুরো ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে।
লাশপুরীর লাশের গল্পে সত্যিকার অর্থেই গল্পের একটা মুগ্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে। এর মধ্যে অপরিসীম আবেগ, কৌতূহল, স্বপ্ন আকস্মিকতা উৎকণ্ঠা বজায় রয়েছে। যা পাঠক সাধারণের মনকে একটা সম্মোহ সীমানায় ধরে রাখতে সক্ষম। তাছাড়া এর কাহিনী চরিত্রে বরাবরই একটা আদর্শবোধ ব্যাপ্ত আছে। এ সুবাদে সেখানে সমাজ মানসের কিছু বিশ্বস্ত চিত্রগাথা পরিস্ফুট উঠার সুযোগ পায়। যা শুধু এদেশীয় সংস্কৃতির আদলে গড়ে ওঠেছে। যেমন মীরা কেন্দ্রিক সারিনা জামান এর ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। মেয়েটির আত্মহত্যা ও এর আনুপূর্বিক ঘটনা যে কাউকে ছুঁয়ে যেতে সক্ষম। সংসারের অভাব-অনটন, বন্ধুবান্ধবীদের নিগ্রহ-নিপীড়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবজ্ঞা, অবহেলা-সবমিলিয়ে মেয়েটির জীবন বিষিয়ে তোলে। এছাড়া সাব্বিরের দাদিবাড়ি গাছতলা গ্রামের নানাবিধ ঘটনা এ গল্পের আড়ম্বরের সাথে বনিত হয়েছে। যা পাঠ করে অনাস্বাদিত জগতের উপমিত আস্বাদন করা সম্ভব। আমি লাশপুরীর লাশের গল্প ও এর লেখক লোকমান তাজ এর পর্যায়ক্রমিক সমুন্নতি কামনা করছি।
-ড. মুহাম্মদ জমির হোসেন
লাশপুরীর লাশের গল্প
অনুপ্রাণন ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
সম্পাদকীয়-
শিল্পী গোষ্ঠীর সমাজ-সচেতনতা ও সামাজিক আন্দোলন
শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধভাবে একমাত্র নান্দনিক সৃজনের ঘেরাটোপে বন্দী না থেকে সমাজে বসবাসের শর্তাবলী ও পরিবেশ একজন শিল্পী ও সাহিত্যিক’কে অন্য যে কোন সচেতন নাগরিকের মতোই একান্তভাবে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উৎসারিত ও গৃহীত সকল মতামত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর কাজে প্রকাশ করতে দেখা যেতে পারে। বিশেষতঃ একজন শিল্পী ও সাহিত্যিক পরিবেশ ও সমাজের ক্ষেত্রে গভীরভাবে সংবেদনশীল হওয়ার কারনে তাদের সৃজনশীল কাজে ও রচনায় সমাজের রীতি-নীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ভাল-মন্দ এবং দোষ-গুণের প্রতিফলন থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু না বরঞ্চ এই থাকাটাই যেন স্বাভাবিক। কিন্তু রাষ্ট্র মত প্রকাশের ক্ষেত্রে নানা রকম সীমা বেঁধে দেয়। এসব সীমার মধ্য থেকেই শিল্প চর্চার বিভিন্ন মাধ্যম ও অবলম্বনের সাহায্য নিয়ে একজন শিল্পী অথবা সাহিত্যিকের যেমন প্রচ্ছন্নভাবে নিজের মতটি প্রকাশ করার প্রচেষ্টা থাকে তেমনই আবার শিল্পী-সাহিত্যিকবৃন্দ দ্রোহী হয়ে মত প্রকাশের ফলে রাষ্ট্রের অথবা কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর কোপানলে পড়ে নির্যাতিত হওয়া এমনকি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে তাদের সহিংস আক্রমণের শিকার হতেও আমরা দেখেছি।
তাই, এখানে প্রশ্ন এটা নয় যে, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের সৃজনশীল কাজে ও রচনায় সমাজের রীতি-নীতি, পরিবেশ, অর্থনীতি ও রাজনীতির ভাল-মন্দ এবং দোষ-গুণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ অথবা প্রচ্ছন্নভাবে তাদের ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিফলন থাকবে কি-না? বাস্তবে প্রশ্নটা হচ্ছে সামাজিক-রাজনৈতিক এবং পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে রাষ্ট্র ও জনগণকে সচেতন করা এবং সেসব সমস্যা দূর করার জন্য সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের ভূমিকা কীভাবে নির্ধারিত হবে? বরঞ্চ, প্রশ্নটা দুটো হচ্ছে-
ক. শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ নিজেরাই কোন সামাজিক সংগঠন করবে কি-না অথবা পেশাজীবীদের অন্য কোন বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনে সম্পৃক্ত হবে কি-না? এবং
খ. স্রেফ শিল্পীদের নিজস্ব অথবা অন্য কোন বৃহত্তর সামাজিক সংগঠনের ব্যানারে সমাজের কোন ন্যায্য দাবী অথবা সমাজের কোন বাস্তব সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পরিচালিত রাজপথের আন্দোলনে ফেস্টুন-ব্যানার নিয়ে নিজেরা সম্পৃক্ত হবে কি-না? এবং
গ. যদি শিল্পী ও সাহিত্যিকবৃন্দ নিয়মিতভাবে কোন সামাজিক সংগঠনমূলক কার্যক্রমে সক্রিয় হয়ে যায় এবং সামাজিক ইস্যুতে রাজপথের আন্দোলনে নেমে পড়ে অথবা সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত হয়ে যায় তাহলে সময় ও মনোসংযোগ দ্বিধান্বিত হয়ে বাধা পড়ে শিল্প ও সাহিত্য চর্চার মান ও গুণাগুণের ক্ষেত্রে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা কোন ক্ষতি বা সমস্যার সম্মুখীন হবে কি-না?
এখানে উল্লেখ্য যে, অন্য সামাজিক সংগঠনের আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা অথবা সংহতি প্রকাশ, ঘড়ে বসে শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিজস্ব সংগঠন করা অথবা ফেস্টুন ব্যানার নিয়ে রাজপথে নেমে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদী নানা উপায়ে একজন শিল্পী অথবা সাহিত্যিকের পক্ষে সামাজিক আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। একজন শিল্পী অথবা সাহিত্যিক সামাজিক আন্দোলনের সাথে কীভাবে যুক্ত হবেন সেটা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এবং এটাও বাস্তব সত্য যে একজন সংবেদনশীল ও সচেতন শিল্পী অথবা সাহিত্যিক ন্যায্য দাবী ও বক্তব্য নিয়ে পরিচালিত চলমান সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তায় আবদ্ধ হয়ে কোনভাবেই নিষ্ক্রিয় এবং নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না।
১৯৬৯ এর গণভ্যুত্থান অথবা ১৯৭১ এর মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলিতে শিল্পী সমাজের সদস্যবৃন্দকে সংগঠিতভাবে ফেস্টুন-ব্যানার নিয়ে আন্দোলনে-সংগ্রামে-মিছিলে যুক্ত হতে আমরা দেখেছি। ৭১’এর স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে এমনকি প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নিয়ে শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মুক্তিযুদ্ধে সংযুক্ত হতে আমরা দেখেছি। এর পর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনেও শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছেন। এসব আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র।
স্বাধীনতার পর শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যেসব সংগঠন গঠিত হয়েছে সংগঠনভেদে সেগুলোর মূল লক্ষ্যই ছিল জোটবদ্ধভাবে শিল্প চর্চা, আলোচনা-সমালোচনা, শিল্পের প্রচার-প্রসার, পরোক্ষভাবে ব্যক্তির প্রচার ও প্রসারলাভের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা থেকে বিপণন কৌশল অবলম্বন করা পর্যন্ত। তাছাড়া, রাষ্ট্রীয়, সরকারী অথবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংবাদ-মাধ্যম, কর্পোরেট অথবা নন-কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পদক-পুরস্কার অথবা আনুকূল্য লাভের জন্য এসব কোন কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠন ও জোটের তৎপরতার সুযোগ গ্রহণ করতেও আমরা দেখেছি। শিল্প ও সাহিত্যকেন্দ্রিক নানা তৎপরতা অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এসব সাংগঠনিক তৎপরতার মাধ্যমে সৃজনশীল অথবা মননশীল শিল্পগুণের মান ও রুচির উৎকর্ষতা লাভের ক্ষেত্রে এসব সংগঠন বিশেষ কোন অবদান রাখতে বিশেষ কোন সাহায্য করেছে বলে এরকম উদাহরণ পাওয়া যায় না। দলীয় অথবা ব্যক্তিগত লাভালাভের বিষয়গুলো সেখানে খুবই নগ্নভাবে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে এবং যার ফলে দেশে মাঝারী মানের শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতাই হয়েছে অত্যন্ত অধিকহারে। অন্যদিকে প্রচার, প্রসার ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মৌলিক, মননশীল ও উচ্চতর মানসম্পন্ন শিল্প ও সাহিত্যকর্ম পাঠকদের কাছে ব্যপকভাবে পৌঁছানোর সুযোগ লাভ করতে পারেনি। এবং যার ফলে সত্যিকার প্রতিভাবান শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা হতাশা থেকে প্রচারবিমুখতা ও আত্মকন্দ্রিকতার ক্ষুদ্র গ-ির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন।
এছাড়া, রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্য চর্চা ও গবেষণা এবং তাঁদের সাহিত্যকর্মকে আধুনিক শিশু-কিশোর ও তরুণদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দেশে কয়েকটি সরকারী-বেসরকারী সংগঠন কাজ করছেন। কিন্তু, রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্যকর্মের আক্ষরিক পঠন ও মুখস্থ করার উপরই এসব সংগঠনকে বেশী জোর দিতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের সাহিত্যকর্মের মাঝে যে মানবিক চেতনা ও যে দার্শনিক নির্যাস রয়েছে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সাথে অধিকহারে দেশের শিশু-কিশোর ও তরুণদের পরিচয় করিয়ে দেয়া খুব জরুরী। কেননা এতে করে দেশের নতুন প্রজন্মের মনের মাঝে মানবিক চেতনা ও সুন্দর রুচিবোধ স্থান করে নিতে পারে। এসব বিবেচনা করে রবীন্দ্র-নজরুলের সাহিত্য চর্চা ও গবেষণার জন্য যেসকল সংস্থা ও সংগঠন কাজ করছেন সেসকল সংগঠন দক্ষতার সাথে তাঁদের কাজের পরিধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে চলুক- এটাই প্রত্যাশা করি।
প্রথম থেকেই শিল্প-সাহিত্যের ত্রৈমাসিক, অনুপ্রাণন, ব্যক্তি, দলীয়, গোষ্ঠী অথবা কর্পোরেট তৎপরতার বাইরে নিজের স্বাধীন অবস্থান রক্ষা করে দেশের নবীন ও তরুণ প্রতিভাবান শিল্পী ও সাহিত্যকদের পরিচ্ছন্ন ও মানসম্পন্ন শিল্প-চর্চার জন্য অনুপ্রেরনা যুগিয়ে এসেছে। সপ্তম বর্ষে পদার্পন করে ‘অনুপ্রাণন’ অবিচলভাবেই ঐ ঘোষিত পথেই তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে চায়। অনুপ্রাণন-এর মূল পৃষ্ঠপোষক অনুপ্রাণন-এর পাঠকেরাই। তাই, বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করতে পেরে অনুপ্রাণন-এর লেখক এবং পাঠকেরা অবশ্যই বিশেষ অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।
সপ্তম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা
অহেতুক মানুষ
কিরণ আকরামুল হক এর “অহেতুক মানুষ” বইয়ের কবিতাগুলি আমাকে পড়তে হয়েছে নানকারণে। প্রথম বই প্রকাশের পর দু’বছর বিরতি দিয়ে কবি নিজেকে প্রস্তুত করেছেন। কবিতার ভেতরের শিল্পকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। রূপক, উপমার সেলাই শিখেছেন। সাথে প্রগতিশীলতার চর্চা থাকায়, ‘অহেতুক মানুষ’ গ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতাই কবিতা হয়ে উঠেছে। সমকালীন চিন্তা, বিষয় ভাবনা, আর পরিমিত নির্বাচিত শব্দ-প্রয়োগে অহেতুক মানুষ গ্রন্থের কবিতাগুলিকে কবি কিরণ আকরামুল হক এর ভাবনার পরিণত বুনন বলা যায়। গ্রন্থখানার দারুণ পাঠকপ্রিয়তা আশা করছি।
-ফিরোজ আহমেদ
অহেতুক মানুষ
আটপুকুরের ফুল
ভূমিকা-
ভেতরটা খালি, গল্পের অভাব, যুতসই প্লট পাচ্ছি না- এমন অবস্থায় সচরাচর বাইরে বের হই। হাঁটতে থাকি। সামনের মোড়টা পার হলেই বিশাল হাইওয়ে। এই হাইওয়ে দিয়ে চাইলে যেকোনো জায়গায় যাওয়া যায়। আমারও ইচ্ছা, যাই।
একা একা বেশিক্ষণ হাঁটা যায় না। একটু আগাতেই, কয়েকগুচ্ছ আলো এসে ভিজিয়ে দেয় অন্ধকারের শরীর। আগ্রহ নিয়ে ঘাড়টা ঘোরাতেই দেখি দুটি যান্ত্রিক চোখ। গাড়িটা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।
এরই মধ্যে টের পাই আমার সাথে আরেকজন। সেও হাঁটছে। ল্যাম্পোষ্টের আলোর সাথে সাথে পাল্টে যাচ্ছে তার শরীর। বুঝতে পারি, তার কিছু বলার আছে। তবুও থামতে ইচ্ছা করে না। নিজের ছায়ার সাথে আমার কথা হয় না, বহুদিন!
সামনে থাকা অনেক কিছুই ইশারা করে! রাতের নিষিদ্ধ সেই সব ডাক, না শুনে পারি না। বৃদ্ধ পাইকর গাছ, একটা চিঠির লাল বাক্স, পাশে ড্রেন, সেখানে জোড় হারানো একপাটি স্যান্ডেল উল্টে পড়ে আছে। আমি ওদের কাছে যাই। নেড়ে চেড়ে পরখ করি, ভেতরে গল্প আছে কী না।
আটপুকুরের ফুল
দ্বিধাগ্রস্ত পা রাখি পথে
ভূমিকাঃ
যে কথা অন্য কোনভাবেই প্রকাশ করা যায় না । যে কথা প্রকাশ করার জন্য কোন মাধ্যমের দরকার হয়ে পড়ে। যে কথা চার দেয়ালের মাঝে গুমরে গুমরে কাঁদে কখনো কখনো। এমনি একদিন বড় দুঃসময় কবিতা এসেছিল আমার ঘরে আত্মার আত্মীয় হয়ে। বন্ধু, সমাজ, সংসার, প্রিয়জন, স্বজন কেউ কোত্থাও একাকিত্বের স্বর শুনতে পায়নি যখন। নিঃসঙ্গতার সংগে মিশে যেতে যেতে যে কথা কবিতা হয়ে উঠেছিল। কবিতায় খুঁজে ফিরেছিল প্রেরণা, প্রত্যাশা বেঁচে থাকবার অবলম্বন। যে কবিতারা চোখে দেখেছিল অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, ধর্ষণ আবার সৌন্দর্যমহিত অবারিত ফসলের মাঠ, চিরসবুজ নিসর্গ, প্রকৃতি, ঋতু পরিবর্তন, মানবতার বন্ধন, দেশ, রাজনীতি, নৈতিক শিক্ষা, কত শৈস্যের দীপ্তমহিত সম্ভার। কত স্মৃতি, চেনা -অচেনার সুস্থ প্রতিভার বিশালতা অন্তর্লীনে ঢেউ তুলে কখন যে গড়ে ওঠে কাব্য হয়ে কে তা জানে! স্বপ্ন তাই নতুন প্রত্যাশায় মেলেছে পাখা। লিখে যাব যতদিন প্রাণ আছে পদচ্ছাপ রেখে যাবার প্রত্যয়ে অর্ন্তদেশের অব্যক্ত বর্ণমালার সুনিপুণ কারিগর হয়ে প্রকৃতি ও প্রেমে।
দ্বিধাগ্রস্ত পা রাখি পথে
ঈশান রাজকুমার
প্রাক-কথন
একটি সফল নাটক উচ্চারণ করে সময়ের সত্য, মানুষের অন্তর্গতে শায়িত থাকা সম্পর্কের সুস্পষ্ট স্বর।
নিজের শরীরে ধারণ করে জীবনের বহুমাত্রিক রং, যাপনের বর্ণমালা।
নাটক ‘ঈশান রাজকুমার’ এমনতর বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।
ইতিহাস-নির্ভর রচনার ক্ষেত্রে লেখকের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনা গুলির জন্য তাঁকে প্রাচীন পুঁথি, নথি এবং মানুষের মুখে মুখে ফেরা কথা ও কাহিনি থেকে নিজের লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়।
এবং এক্ষেত্রে লেখক হয়ে ওঠেন ভ্রামণিক। সময়ের সম্মুখে নয়, তিনি যাত্রা করেন অতীত সময়েরদিকে। পৌঁছাতে হয় পার-হয়ে-আসা-সময়ের হলুদ বৃত্তান্তগুলির কাছে। যে-লেখক তাঁর পুরোনো জন্মকালের মুহূর্তগুলিকে যত নিবিড় করে ছুঁতে পারেন, তিনিই তত সফলভাবে ঐতিহাসিক সত্যকে অধিগত করতে পারেন। সত্যের সেই বৃত্তান্তকে হাজির করতে পারেন তাঁর পাঠকের কাছে।
ইকবাল রাশেদীন শক্তিশালী কবি। কবির মননজাতবোধ এবং সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি দিয়ে তিনি ছুঁয়েছেন দু’শো পঞ্চাশ বছর আগের পৃথিবীকে। নিজের পরিশ্রমী গবেষণা দিয়ে তুলে এনেছেন ইতিহাসের বুকে ধুসর হয়ে যাওয়া ঘটনাক্রমকে। কবি থেকে নাট্যকার হয়ে ওঠা খুব সহজ কাজ নয়, সেই অসহজ কাজটিই ইকবাল করে দেখিয়েছেন তাঁর ‘ঈশান রাজপুত্র’নাটকে।
আমার মনে হয়েছে, নাটকের জাহাজটি একটি দেশ এবং ঈশান রাজকুমার সেই দেশের যোগ্য নেতৃত্ব। এবং সেইসাথে নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র ঈশান আসলে ডানামেলা এক পাখি। যার দেশ নেই, সীমান্তনেই। আছে কেবল পৃথিবীময় একজগত বাড়ি। সেই বাড়ির বাসিন্দা হয়ে অন্তরমহল আর অন্দরমহলের কথাই সে উচ্চারণ করেছে আত্ম মগ্নস্বরে।
ইকবাল রাশেদীন কবি বলেই হয়তো এই আত্মমগ্নস্বরের নির্মাণে তিনি অনায়াস। এবং নাট্যকার হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব এখানেই যে, এই আত্মমগ্ন স্বর শুধু তাঁর ‘আত্মমগ্নস্বর’ হয়েই থাকেনি, পাঠক/দর্শক ও খুঁজে পাবেন তার নিজের মতো করে নিজের ‘আত্মমগ্নস্বর’।
রেহান কৌশিক
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
১৬ ডিসেম্বর ২০১৭
ঈশান রাজকুমার
অনুপ্রাণন ৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
মাতৃভাষা, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়
বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সমাজের অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয় মুছে দিয়ে চিরকালের জন্য নিজ শাসন ও শোষণের আওতায় নিয়ে আসার জন্য এক একটি জাতি ও উপজাতির নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতিকে আক্রমণ করে দুর্বল করে দিয়ে সুকৌশলে একক একটি ভাষা ও সংস্কৃতি জাতিতে জাতিতে চাপিয়ে দেয়া- সাম্রাজ্যবাদী শোষণ বিস্তারের প্রাথমিক পরিকল্পনারই একটি অপকৌশল। আধুনিক বিশ্বে বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করা ও বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য ’৫২ এর ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়, যে অধ্যায়ের মধ্যে আমাদের ভাষা, সাহিত্য শুধু নয়, আমাদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব এবং আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের মহান সংগ্রামেরই ঐতিহাসিক সূত্রপাত। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের স্মরণে প্রতিবছর ফেব্রুয়ারিতে অমর একুশে বইমেলা- বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তথা বাঙালী চেতনাকে সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করে তোলার কাজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আমাদের জাতীয় জীবনে অমর একুশে বইমেলার অপরিসীম ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে আমাদের অনুধাবন করতে হবে এবং এই বইমেলার গুণগত মান এমনভাবে পরিকল্পিত ও সুসংগঠিত করতে হবে যেন এর সুফল সারা বছর জুড়ে আমাদের জাতীয় জীবনে সফলভাবে কার্যকরী থাকে।
ভাষা, শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির উৎকর্ষ সাধনের যে কোন প্রচেষ্টায় দেশের গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মানসম্পন্ন কাজে রূপান্তরিত করাটাই জরুরী। তাছাড়া, প্রতিনিয়ত নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটানো এবং সেসব নতুন নতুন চিন্তার বাস্তবায়ন একটি জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে সুদৃঢ়ভাবে সচল রাখতে এবং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন মোকাবেলা করতে সবল ও সক্ষম করে তুলতে পারে। একুশে বইমেলাকে ঘিরে সেসব কাঙ্ক্ষিত রূপান্তর ঘটাতে আমরা কতটুকু সক্ষম হচ্ছি- এটাই আমাদের সামনে মূল প্রশ্ন। গণমানসের অনুবাদই প্রতিভার একমাত্র ধর্ম নয়। গনমানসের সংগঠনে সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে উপযোগী রূপান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টাই একুশে বইমেলার মতো এই বিরাট কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। কিন্তু, আমরা এই বিরাট কর্মযজ্ঞের মাঝে গনমানসের সংগঠনে রূপান্তর ঘটার মত সৃজনশীল কর্মসূচি গ্রহণ করতে দেখি না। আত্মকেন্দ্রিক পুনরাবৃত্তির মধ্যে একুশে বইমেলাকে বন্দী রাখার মত অপচয় কীভাবে বন্ধ করার যায়- এ নিয়ে আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার। সত্যের এই পরিণতি মনে রাখাটা খুবই জরুরী- যে সাধনার অগতি বন্ধ্যত্ব আনে, সেই বন্ধ্যত্বের মাঝেই স্বকীয়তা, স্বাতন্ত্র্য, আত্মমর্যাদা ও আত্মপরিচয়ের বিনাশ ঘটে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, একটি জাতির নিজস্ব প্রতিভা ও সৃজনশীলতার চর্চাকে বিপথে পরিচালিত করার অপচেষ্টা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ সবসময় চটকদার কর্মসূচি আমাদের মাঝে হাজির করবে।
গত শতাব্দীর শেষভাগে, নিয়ন্ত্রিত শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চা বনাম মুক্ত ও স্বাধীনভাবে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার সুফলতা ও কুফলতা নিয়ে বিতর্কের এক রকম অবসান ঘটায় এখন দেশে দেশে মুক্ত ও স্বাধীন শিল্প ও সাহিত্যের চর্চার পক্ষেই জনমত গড়ে উঠেছে। কিন্তু, মুক্তচিন্তার প্রকাশের কারনে শাসক শ্রেণি বিব্রত হয় বলে শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রণ একেবারে উঠে যায় নি। সেন্সরশিপ আরোপ এবং গত কয়েক দশকে মুক্তচিন্তা চর্চাকারীদের উপর কট্টরপন্থীদের সশস্ত্র আক্রমণ ছাড়াও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নানা বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ হতে দেখা যাচ্ছে। এসব প্রচেষ্টা শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথে বাধা। শত শত বছরের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে নতুন ও মুক্ত চিন্তার চর্চা ও সম্পৃক্ততা ছাড়া শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে গনমানুষের নান্দনিক অভিব্যক্তি বাধাহীন বিকাশ লাভ করে না। নিয়ন্ত্রিত বিকাশ যে বাস্তবে ঘটে না এবং অবশেষে বন্ধ্যত্ব ও স্থবিরতার কবলে পরে ধ্বংস হয়ে যায় এর ঐতিহাসিক প্রমাণ যেমন দুঃখজনক তেমনই বাস্তব।
কিন্তু, এটাও মনে রাখতে হবে যে মুক্ত, স্বাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার নামে নৈরাজ্য একেবারেই কাম্য নয়। বলতে গেলে, দেখা যাচ্ছে যে সাহিত্য চর্চা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে দুধরনের প্রবণতা এই ক্ষেত্রটিকে দারুণ ক্ষতির সামনে দাড় করিয়েছে। কর্পোরেট পৃষ্ঠপোষকতা যতই মান বিচারে নিরপেক্ষতার কথা বলুক না কেন, বাস্তব কিন্তু তা বলে না। ফলে এমন একটি সুবিধাভোগী শিল্পী ও সাহিত্যিক চক্র তৈরি হচ্ছে যাদের তৈরি শিল্প-সাহিত্যের মান সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে ভুল বার্তা দিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটি গড় মানের মধ্যে আটকিয়ে রাখা হচ্ছে। ফলে প্রতিভাবান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের মাঝে এমন একটা হতাশা তৈরি হচ্ছে যে তাদের হাত দিয়ে বাংলা শিল্প ও সংস্কৃতিতে যে উচ্চ স্তরের বিকাশ ঘটানো সম্ভব ছিল সেই পথ দুঃখজনকভাবে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটছে, সেটাও খুব দুঃখজনক। একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে এর উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে একদল শিক্ষানবিস লেখক নিজ খরচে বই প্রকাশ করে এবং তাঁর পক্ষে দল পাকিয়ে নিজেকে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রচারনায় লিপ্ত হচ্ছেন। এসব সাহিত্যকর্ম একেবারেই মানসম্পন্ন নয় ফলে প্রজন্ম বাংলা সাহিত্যের মান সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রাপ্ত হচ্ছেন। অনুপ্রাণন আশা করে যে, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে মননশীল, সৃজনশীল ও মানসম্পন্ন শিল্প ও সাহিত্যের চর্চা ও সাধনার পক্ষে গভীর সচেতনতা নিয়ে একটি মুক্ত ও স্বাধীন প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠবে।
সপ্তম বর্ষ প্রথম সংখ্যা
অনুপ্রাণন ৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
সম্পাদকীয়
অনুপ্রাণন: ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়
গত নভেম্বর ২০১২ থেকে অনুপ্রাণন ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সাহিত্য ও শিল্প বিভাগের বিবিধ সৃজনশীল ও মননশীল লেখায় সমৃদ্ধ হয়ে নিয়মিত ভাবেই প্রকাশিত হয়ে আসছিল। কিন্তু, পঞ্চম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যাটি বৃহৎ কলেবরে অর্থাৎ নিয়মিত ১৬ ফর্মার বদলে ১৯ ফর্মা আকারে প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তী ৫ টি সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। সম্পাদকের অসুস্থতা ছাড়াও অলিখিতভাবে সম্পাদনা পরিষদের যে সদস্যবন্ধুটি পত্রিকার কাজে অফিস সমন্বয়কের গুরুদায়িত্ব পালন করছিলেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক কাজ চালিয়ে যেতে তিনি নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে থাকলে পত্রিকার কাজে ছেদ পড়তে থাকে। তাছাড়া সম্পাদনা পরিষদের আর একজন বন্ধু অন্য একটি অনলাইন পত্রিকার কাজে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে তাঁর পক্ষে অনুপ্রাণন পত্রিকায় প্রয়োজনীয় সময় দেয়া আর সম্ভব হয়ে উঠছিল না। সম্পাদনা পরিষদের অন্য আর একজন সংগঠক পর্যায়ের সদস্য পত্রিকার চাইতে গ্রন্থ প্রকাশনায় বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়ায় প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রাণন পত্রিকাটি প্রকাশের কাজে লোকবলের এক বিরাট সংকট দেখা যায়।
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে- ২০১২’এর নভেম্বরে অনুপ্রাণন ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশ করার উদ্যোগ যারা নিয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যার যার নিজ অবদান ও স্বাক্ষর রাখার উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রম ও ব্যক্তিগত অনুদানের ভিত্তিতে পত্রিকাটির প্রকাশনার কাজের যাবতীয় কাজ ও ব্যয় নির্বাহ করার অভিপ্রায় গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, সমাজ সংস্কৃতিতে এবং বিশেষ করে তরুণদের মনের মাঝে মানবতা, সহমর্মীতা, সৃজনশীলতা, মননশীলতা, শিল্পরুচি, নান্দনিকতা এবং মুক্তচিন্তার চর্চার জানালাটাকে উন্মূক্ততর করার কাজে নিয়োজিত অনুপ্রাণনের এই প্রচেষ্টা যেন বাধাহীন হয় এবং কোনভাবেই যেন প্রতিষ্ঠা ও কর্পোরেট ভোগবাদীতার কূট সাংস্কৃতিক আবর্তে পড়ে দিক হারিয়ে না যায়।
যশ ও প্রতিষ্ঠার মোহ যখন শিল্পীকে পেয়ে বসে তখন শিল্পচর্চা তপস্যা অথবা সাধনা থাকে না। কিন্তু, এটাই বাস্তব যে তপস্যা ও সাধনা ছাড়া শিল্পের উৎকর্ষতার শীর্ষ স্পর্শ সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রতিষ্ঠা ও কর্পোরেট ভোগবাদের বলয়ে যেসব শিল্প-সাহিত্য চর্চা ও উদ্যোগ ফেনার মত আমাদের চারদিক ভরিয়ে তুলছে সেসবের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কী কোন সন্দেহ থাকা উচিত?
বছরখানেক বন্ধ থাকার পরও যখন আমরা অনুপ্রাণনের এই সংখ্যাটি প্রকাশের উদ্যোগ নেই তখন আমরা আমাদের পত্রিকার পাঠক, লেখক ও শুভান্যুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অভূতপূর্ব সারা পেয়েছি। এই সারা থেকে এই বিশ্বাস আমাদের জন্মেছে যে, আমরা যে পথ অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে চাই সেই পথে বাস্তবেই সঙ্গ-সাথীর আমাদের কোন অভাব নেই। এখনও আমাদের দেশের তরুণ সমাজের একটি বিরাট অংশ মিথ্যা যশ, প্রতিষ্ঠা ও কর্পোরেট ভোগবাদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে শিল্প-সাহিত্যের মানবিক ও নান্দনিক চর্চা অব্যহত রাখতেই অধিক আগ্রহী। তাই, লেখা আহ্বানে যে সংখ্যক মানসম্পন্ন লেখা আমরা পেয়েছি সেগুলো দিয়ে অনায়াসেই দুটো সংখ্যা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল। চলতি সংখ্যার জন্য লেখা বাছাই করতে গিয়ে আমাদের অনেক সময় দিতে হয়েছে এবং স্থান সংকুলানের অভাবে প্রায় অর্ধেক লেখাই পরবর্তী সংখ্যার জন্য রেখে দিতে হয়েছে।
লেখা বাছাই করতে গিয়ে আবারো আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে যে, সাহিত্য আলোচনা ও সমালোচনা বিভাগে আমরা যথেষ্ট সমৃদ্ধ লেখা পাচ্ছি না যেখানে পেশাদার সমালোচকের কলমের স্পর্শ আরো তীক্ষè অথচ আরো গঠনমূলক হতে পারে। বিশেষ করে কবি ও কবিতা নিয়ে আমাদের আরো তীক্ষè, তীব্র ও গঠনমূলক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কেননা সাহিত্য জগতে কবি ও কবিতার সংখ্যা যতই বাড়ছে কিন্তু আগ্রহী কবিতার পাঠকের সংখ্যা যেন সেই তূলনায় বৃদ্ধি হচ্ছে না। মনে হয়, কবি ও পাঠকের মাঝে বোধ, অনুভব ও ভাষার কোন একটা অন্তর থেকে যাচ্ছে যে অন্তরটি ঘুচে যাওয়া অত্যন্ত জরুরী কেননা বোধ করি, মূলত কবিতার মধ্যেই রয়েছে তরুণ সমাজের জন্য ভবিষ্যতের বিশেষ বার্ত্তা। অর্থাৎ সাহিত্যের সত্যপাঠ।
দেশে এখন হেমন্ত ঋতু। হাওরের অকাল বন্যা ও দেশব্যাপী অতিবৃষ্টির ফলে ফসলহানী ঘটায় এবছর দেশের সামগ্রিক সমাজ জীবনে খাদ্যের ঊর্ধ্বমূল্য সকল মানুষকেই কষ্ট দিয়েছে। হেমন্তের নতুন ফসল যেমন কৃষকের ঘড়ে ঘড়ে জীবনে ঘুরে দাড়ানোর বার্ত্তা দিয়ে যাচ্ছে- দীর্ঘ বিরতির পর অনুপ্রাণন ত্রৈমাসিকের এই সংখ্যাটি এ-বছর অনুপ্রাণনের ঘুরে দাঁড়ানোরই প্রতীক ও স্বাক্ষর হোক- এটাই আশাবাদ।
ষষ্ঠ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা





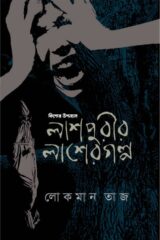


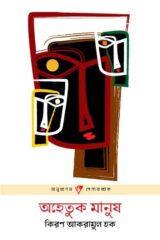










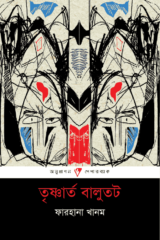
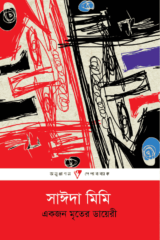
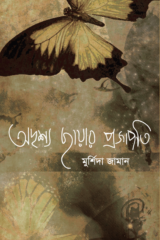
অন্তমিলের কবিতাটি ভালো লাগলো।...
রেজিস্ট্রার করে আপনার লেখা পোস্ট করুন।...
লেখক...