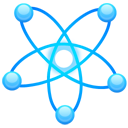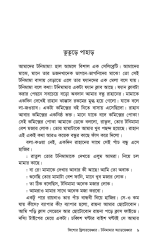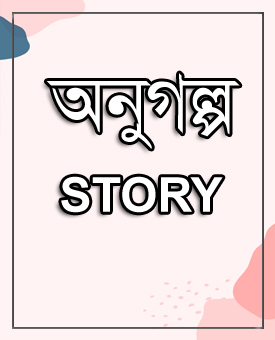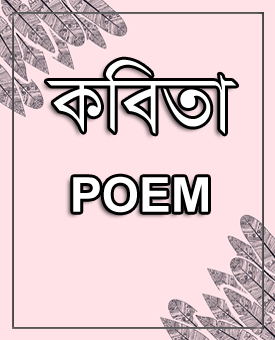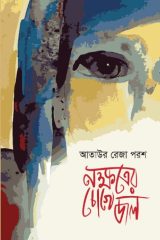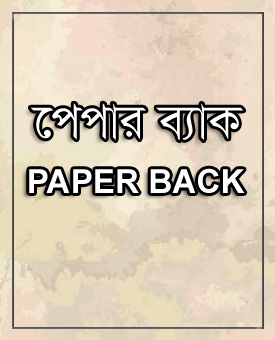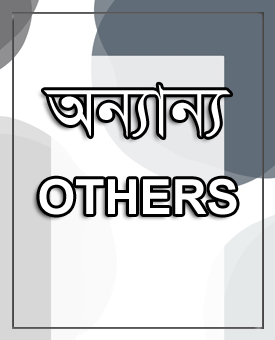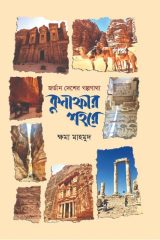Latest News
অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ২০২৫- দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত
অনুপ্রাণনের ‘সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কবি ও কবিতা সংখ্যা’র মোড়ক উন্মোচন
অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন ২০২৫ অনুষ্ঠিত- পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতা বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণের জমকালো আয়োজন
কবি রফিক আজাদ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন বাংলার দুই কবি – কবি ফারুক মাহমুদ ও কবি ফেরদৌস নাহার।
অনুপ্রাণন লেখক সম্মেলন – ২০২২
নতুন প্রকাশিত বইসমূহ
ফেসবুক রঙ্গ রসিকতা – গ্রন্থনা ও সম্পাদনা শফিক হাসান
ফেসবুক কি সময় নষ্ট করায়, দিয়ে যায় ক্লান্তি-হতাশা?
না; ফেসবুকের প্রাপ্তিও কম নয়। ইতিবাচক ব্যবহার করা গেলে। বিনোদনের দুনিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালি জন্ম থেকে রসিক। কথাবার্তা থেকে যাপিত জীবনের কাজ-কর্মে রসবোধের পরিচয় মেলে। ফেসবুকও হয়ে উঠছে রসাধার।
কেউ কেউ স্ট্যাটাসে এমন সব কথা লেখেন। হা হা হা কিংবা খিলখিল করে হেসে উঠতে হয়। চেপে রাখার সুযোগ নেই। বাছাইকৃত মজাদার ও রসাত্মক ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে বইটি। খ্যাতিমান মানুষ থেকে সাধারণের মধ্যে যে রসবোধ প্রখর, প্রমাণ মিলবে এতে।
পাঠককে নিষ্কলুষ হাসি উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টায় মেতেছেন শফিক হাসান। উদ্যোগ সার্থক নাকি অন্যকিছু সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে বইয়ের পাতায় পাতায়।
Facebook Rongo Rosikota - Collection & edited by Shafique Hasan
মায়াবী ট্রেন – মৃন্ময় মনির
ভ্রমণ অনির্দিষ্ট। জন্ম থেকেই তার শুরু। মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত একশো বছরের ভেতরেই তা ঘোরাফেরা করে! বেড়ানোর জন্য অনেক যন্ত্রযান রয়েছে কিন্তু ট্রেনের মতো এমন মায়াবী ভ্রমণ আপনি কোথাও পাবেন না! অবশ্য আপনি বসে থাকলেও আপনার পথচলা একদিন শেষ হবেই, প্রাণীর জন্য দ্বিতীয় কোনো পথ এখনো খোলা নেই।
Mayabi Train - Mrinmay Monir
রাঙাপ্রভাত – পিন্টু রহমান
মানুষের ইতিহাস
মূলত স্বপ্ন আর সংঘর্ষের যুগলবন্দিতে রচিত হয় ইতিহাস।ইতিহাসের পথ ধরে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য থেকে আধুনিক নগরঅব্দি জীবন ও যুদ্ধ সমান্তরাল রেখায় পথ হেঁটেছে। মানুষ তথাপি বৃত্তাবদ্ধ থাকেনি; স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্ন বুনেছে, স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে কাল থেকে কালান্তরের পথে অভিযাত্রী হয়েছে। হোঁচট, ভাঙন, মোহভঙ্গ— সবকিছু পেরিয়ে মানুষ আবার দাঁড়িয়েছে নতুন এক ভোরের প্রত্যাশায়। আর সেই প্রত্যাশার গর্ভেই জন্ম নিয়েছে অনিবার্য লড়াই। সাতচল্লিশ, বায়ান্ন, একাত্তর কিংবা চব্বিশেরগণঅভ্যুত্থান এক-একটি রক্তাক্ত অধ্যায়, যেখানে কাঁচা রক্তরেখায় আঁকা হয়েছে জীবনের ক্যানভাস। ব্যক্তিগত বেদনা ও সামষ্টিক আর্তনাদ মিলেমিশে তৈরি করেছে সময়ের ভাষ্য। হংসমিথুনের মতো ভেসে বেড়ানো অবচেতন মন কখনো প্রেমে, কখনো প্রতিবাদে, কখনো নিঃসঙ্গতায় আশ্রয় খুঁজেছে। ঘোর অমানিশা যত গভীরই হোক মানুষ জানে অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়। তাই আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্মিলনে লেখা হয় জীবনমুখী গল্প। এখানে যুদ্ধ আছে, ক্ষত আছে, পরাজয় আছে; আবার আছে প্রতিরোধ, ভালোবাসা ও নতুন সকালের স্বপ্ন। “রাঙাপ্রভাত” তাই কেবল একটি ভোর নয়, এটি মানুষের অবিনাশী আশার নামাবলি।
পিন্টু রহমান
কথাসাহিত্যিক
Rangaprovat - Pintu Rahman
হারানো দিনের প্রেম-অপ্রেমের গল্প – সাইদ হাসান দারা
তখন আমি স্মৃতিবিধুরতার কাছে পরাজয় বরণ করে প্রথমবারের মতো সাহস করে আমার অবাস্তব প্রেমের অলীক দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে লাগলাম। ফলে সর্বপ্রথমে আমার মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলার বুড়ি আপার কথা। অতঃপর বেঁচে থাকার স্বার্থে আমি একদিন সকলের অমতে তাকেই দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ে করে ফেললাম।
তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে সক্ষম হলাম, ভালোবাসা সম্পর্কে পূর্বে-যতোটা ভেবেছিলাম, সে-আসলে তারচেয়ে আরও অনেক বেশি কিছু পেয়ে চায় এবং সে নিজেকে ছাড়া কিছুই দেয় না পক্ষান্তরে অন্যের থেকে কিছুই গ্রহণ করে না-ভালোবাসার গল্প।
মানব-মানবীর জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা প্রেম-সংক্রান্ত ঘটনাবলি বা তার আখ্যান-উপাখ্যান যে কত ভিন্ন প্রকারের এবং ভিন্নধর্মী হতে পারে। আমার বিশ্বাস-ভালোবাসার তত্ত্ব অনুসন্ধানী পাঠক এবং প্রেম-সংক্রান্ত গবেষকগণ এই ‘হারানো দিনের প্রেম-অপ্রেমের গল্প’ গ্রন্থে তার সন্ধান অবশ্যই পাবেন।
Harano Diner Prem-Apremer Golpo - Sayeed Hasan Dara
কিশোর থ্রিলারভেঞ্চার : টনিমামার অ্যাডভেঞ্চার – ইউনুস আহমেদ
আমাদের টনিমামা! হাল আমলে বিশাল এক সেলিব্রেটি। আমাদের মাঝে, মানে তার ডজনখানেক ভাগনে-ভাগনিদের মাঝে। তো সেই টনিমামা বাসায়। বেড়াতে এলে তার ফ্যানদের এক মেলা বসে যায়।
মজার সব কাণ্ড ঘটে। টনিমামা বলে কথা! টনিমামার একটা ফ্যান ক্লাব আছে। ফ্যান ক্লাবটা করার পেছনে সবচেয়ে বড়ো অবদান আমার বন্ধু রাহানের। মামাকে একদিন দেখেই রাহান ঝাঁক্কাস রকমের মুগ্ধ হয়ে গেলো। যাকে বলে লা-জওয়াব। একটা কমিজে বই নিতে বাসায় এসেছিলো রাহান কমিজ্ঞে পোকা! সেই কমিজে পোকা আমাকে ডেকে বললো, রাতুল, তোর টনিমামা বেশ মজার লোক। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। রাহান এই একই কথা আরও কয়েক বন্ধুর কাছে ফাঁস করে দিলো। তো সেই টনিমামাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বন্ধুরা, প্রায়ই আমরা আমরা অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে তোমরাও তবে চলো…
কিশোরদের উপযোগী এরকম আটটি অ্যাডভেঞ্চার গল্প নিয়ে ইউনুস আহমেদের থ্রিলারভেঞ্চার গল্প সংকলন-‘টনিমামার অ্যাডভেঞ্চার’।
Kishore Thrillerventure : Tonimamar Adventure - Younus Ahmed
টাইম মেশিন – শাপলা সপর্যিতা
প্রতিরাতে ঘুমাতে যাবার সময় মায়ের কাছে রাজকন্যা রাজপুত্র আর দেওদৈত্যর কিসসা কাহিনী শুনতো না মেয়েটি। শুনতো মায়ের ছোটবেলার প্রকৃতিঘেঁষা স্মৃতিময় সব সত্য গল্পগুলো। এসব শুনতে শুনতে ঢাকা নামক ইট কাঠ কংক্রিটের শহরে বড় হয়ে ওঠা অথচ প্রকৃতির সঙ্গলিদায় বিভোর এক বাংলাদেশী কিশোরীর পৃথিবীবিখ্যাত গবেষক হয়ে উঠার গল্পের শুরু। সে মেতে উঠে টাইম মেশিন আবিষ্কারের নেশায়। টাইম মেশিনে চড়ে যাবে মায়ের ছোটবেলায়, ভোরের হালকা আলো ফুটতে না ফুটতেই ছুটে যাবে শেফালিতলায়, পেয়ারা বাগানের অন্ধকারে বাঁদূরঝোলা দেখবে, পাহাড় জঙ্গলে খুঁজবে সবুজ পেয়ারা, ধানক্ষেতের আইলে দেখবে সাদা বকের অলস দাঁড়িয়ে থাকা। ভরা বর্ষায় পুকুর উপচে ওঠা পানিতে ভরে গেলে ঘাসের মাঠ থেকে ছোটমাছ ধরবে নিজের হাতে-এই তার স্বপ্ন। সময় বয়ে যায়। বিয়ে সংসার করা হয় না। জীবনের মাঝবেলাতে এসে বিপুল পরিশ্রম আর গভীর মায়ায় তৈরি করতে পারে টাইম মেশিন। তাতে চড়েও বসে। টাইম মেশিনে সফল ভ্রমণের মাধ্যমে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেয় এই বাংলাদেশী নারী। কিন্তু ২০৩৭ সাল থেকে ভ্রমণ করে ২০০৭ সালের পর আর পিছে যেতে পারে না টাইম মেশিন? কেন যেতে পারে না? ঐখানেই যে পড়ে আছে মায়ের। প্রকৃতি ঘেঁষা অতীত। যা ছুঁয়ে দেখবে বলেই টাইম মেশিনের আবিষ্কার। আসলে কি সে যেতে পেরেছিল মায়ের ছোটবেলাটাতে? পেয়েছিলো কি সেই বিপুল রহস্যময় সুন্দর প্রকৃতির সঙ্গ? যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনে মানুষের প্রকৃতিলগ্ন হবার যে একাগ্র ও নিবিড় ধ্যান তারই গল্প নিয়ে ‘টাইম মেশিন’।
Time Machine - Shapla Shawparjita
গুপ্তহত্যা… অতঃপর – শাপলা সপর্যিতা
কোনো কোনো মাঝরাতে কেন খালার পোষা কুকুর বব অস্থিরভাবে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। পোশা ময়নাটাও তখন অস্থির। কিন্তু কেন? শত বছরের পুরানা বাড়িটি ফেলে ভারতে চলে যাবার সময় হিন্দু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন রাশেদের খালু। বাড়ির সামনে খোলা লন। তারপর বিশাল প্রশস্ত সিঁড়ি পার হয়ে উঠেই টানা বারান্দা। বারান্দায় চওড়া পিলারগুলো যে রাশেদ কোনোদিন দুহাত ধরে এগুলোর বেড় পেত না। বাড়ির উপরে সিংহ মূর্তিটি খালু ভেঙে ফেলে সেখানে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন। বাড়ির সদরদরজা পার হয়ে সামনে আগানোর পথে প্রতি বিকালে অনেক অনেক পায়রা আসে। খালা ওদের খাবার দেন। খুঁটে খায়। রাত হতে হতে ওরা আবার নিজেদের বাসায় চলে যায়। কিন্তু পায়রাগুলো আসলে কারা? ওরা কি পাহারা দেয় এ বাড়িতে? দুটি পায়রা কেন সদর দরজার বাইরে থেকে গুলি করে মারা হলো? খালা পায়রাগুলোকে নিতে দিলেন না। তারপরই কী কী অঘটন ঘটতে শুরু করল বাড়িটিতে? সামনে খোলা পথে একটা বড়ো লম্বা তালগাছ। তার ওপর থেকে মাঝরাতে কেউ একজন নেমে আসেন। খালার সাথে কি গোপন কথা তার? কি গোপন শলাপরামর্শ করেন খালা ওর সাথে? কে বা কারা কাজের ছেলে রহিমের ওপর চড়াও হয় রাতের বেলা! মধ্যরাতে ঘরের ভিতর মেরে ওর হাড়-মাংস একাকার করে ফেলে। হঠাৎ কেন বাড়ির সব আলো অন্ধকার হয়ে যায়! বাড়ির বড়ো ছেলে ফাইয়াদকে কেন কাজের ছেলে রহিম পিছনের পুকুরে ফেলে বুকের উপর উঠে বসে পানিতে ডুবিয়ে মারতে চায়? রহিমের গায়ে এমন বোটকা গন্ধ কীসের? রহিমের গলায় এ কার অচেনা স্বর? তবে কি কোনো অতৃপ্ত আত্মা রহিমের উপর চড়াও হয়ে বসেছে? এই বাড়ির মানুষের উপর ওদের কেন এত রাগ? ওরা কারা? কুলকিনারা কি করা যাবে এ রহস্যের!
Gupto Hotya... Otohpar - Shapla Shawparjita
গল্পগুলি পুচ্চিদের – মুহাম্মদ ফরিদ হাসান
মুহাম্মদ ফরিদ হাসান বহুমাত্রিক প্রতিভার নিরবচ্ছিন্ন কুশিলব। সাহিত্য গবেষণা ও বিশ্লেষণসহ মৌলিক সৃষ্টিকর্মে তাঁর ভূমিকা অনবদ্য। কবিতার পথে তাঁকে দেখা গেলেও গদ্য তাঁর প্রধান ক্ষেত্র। সবকিছুর পাশাপাশি ফরিদ ছোটদের গল্পও লেখেন, যা দেখে অভিভূত হতে হয়। চমৎকার গদ্যে একেবারে শিশু পাঠকের জন্য তার গল্প নির্মাণকৌশল অতুলনীয়। তার ছাপ দেখতে পাচ্ছি ১২টি গল্প নিয়ে ফরিদের ‘গল্পগুলি পুচ্চিদের’শিশুতোষ গল্পগ্রন্থে। ছোট পরসরে, ছোট-ছোট কোমল সহজ বাক্যবন্ধনে রচিত এই গ্রন্থের প্রতিটি গল্পই স্বতন্ত্র চমক।
একদম শিশুদের নিয়ে, তাদের জন্য সুখপাঠ্য ১২টি গল্প, বিচিত্র বিষয়সমৃদ্ধ ‘গল্পগুলি পুচ্চিদের’। গল্পে এসেছে একদম শৈশবের চঞ্চলতা, স্কুল ও ক্লাসরুম খুনসুটি, বন্ধুদের ছোট-ছোট দ্বন্দ্ব ও রেষারেষি, পাখি, প্রজাপতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্পর্ক আর ভৌতিক, জাদু বা স্বপ্নের বিষয়াবলি। ছোটদের জন্য চিরাচরিত গল্পে প্রবেশের আকর্ষণ ধরে রাখার মশলাপাতিও আছে গল্পগুলোতে।
প্রথম গল্প ‘জাদুর বাংলা বই’, ‘রাশেদ ও নীল ভূত’, ‘পার্থ রহস্য’-সহ প্রতিটি গল্পই হালকা রহস্য, একটু একটু চমক আর গল্পের উপাদানে হয়ে উঠেছে ছোটদের প্রকৃত খাঁটি সাহিত্য- যাকে আমরা বলি শিশুসাহিত্য।
প্রকৃত শিশুতোষ গদ্যের এখন আকাল চলছে আমাদের সাহিত্যে। এরকম সময় মুহাম্মদ ফরিদ হাসানের শিশুতোষ এই গল্পগ্রন্থটি মেঘে ঢাকা আকাশে একটুকরো আলোক। শুধু শিশু-কিশোর নয় এই বইটি তাদেরও পড়া উচিত যারা শিশুর জন্য নিখাঁদ একটি সাহিত্য ডোমেন-এর স্বপ্ন দেখেন।
অভিনন্দন মুহম্মদ ফরিদ হাসানকে। সেই সঙ্গে প্রকাশককেও।
-ফারুক হোসেন
শিশসাহিত্যিক ও ছড়াকার
Golpoguli Puchchider - Muhammad Farid Hasan
শাড়ি ও অন্যান্য গল্প – আমিনুল ইসলাম সেলিম
জীবন হয়তো এক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষারই নাম। হয়তো বায়োস্কোপ-দৃশ্যের মতোই রঙিন অথচ ক্ষণস্থায়ী, স্বপ্নীল অথচ আশাভঙ্গুর। তবু মরীচিকার মতো রহস্যময় জীবনের পেছনে মানুষ ছুটে বেড়ায় ক্লান্তিভোলা পথিকের মতো। হাঁটতে হাঁটতে কখনো ঠিক পথে যায়, কখনোবা পথেই পথ হারায়। এভাবে নানা বাঁক ও বক্রতা পেরিয়ে বারবার জীবনের কাছে পৌঁছাতে হয়। গোলাপের মতো দেখতে সুন্দর জীবন কখনো কখনো এতো কদাকার দেখায় যে, তখন চমকে উঠতে হয়। দেখা যায় যে, ওটা আসলে গোলাপ নয়, গোলাপের আকৃতি।
কিংবা মানুষ যেভাবে ভাবতে চায় না, যেভাবে দেখতে চায় না নিজের জীবনছবি, সেভাবেই তাকে দেখতে হয়, সে জীবনই তাকে বেছে নিতে হয়। জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত কোণে দাঁড়িয়ে অবলোকন করতে হয় নিজেরই প্রতিকৃতি। এ কি জীবনের অনিবার্যতা, নাকি পরাজয়? এ কি স্বপ্নভঙ্গ, নাকি দুঃস্বপ্নের ঘোরটোপ?
যাপিত জীবনে বহুমুখি প্রশ্নের গোলকধাঁধায় ক্লান্ত হয় কোনো কোনো মানুষের জীবন। কখনোবা ক্লান্তিহীনতাও পায় নবপ্রাণ।
এ রকম নানামুখি জীবনের গল্প নিয়ে আমিনুল ইসলাম সেলিম প্রথমবার হাজির হয়েছেন পাঠকের সামনে।
Shari O Anyanya Golpo - Aminul Islam Selim
যেতে চাও যাও – রওশন রুবী
‘যেতে চাও যাও’- ভালোবাসা, জীবনসংগ্রাম এবং মানুষের অন্তরযাত্রা নিয়ে রচিত এক শক্তিশালী উপন্যাস। এহসানুল হক একজন নীতিবান, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ। ছোটবেলা থেকেই তার ভেতরে আছে সততা, সহমর্মিতা ও অন্যের পাশে দাঁড়ানোর সহজাত মন।
জীবনের পথে তিনি দেখেছেন ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং মানুষের বহুমুখী রূপ। তবু তিনি নিজের নৈতিক অবস্থান থেকে কখনো সরে যাননি।
এক সময় গভীর ব্যক্তিগত ক্ষত তাকে ভেঙে দেয়, কিন্তু সে ভাঙন থেকেই এহসানুল নতুনভাবে নিজেকে গড়ে তোলেন। হারানোর বেদনাকে শক্তিতে পরিণত করেন; জীবনজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্দীপ্ত করে, আর ব্যর্থতা তাকে পথ দেখায়। তার কাছে ভালোবাসা শুধু অনুভূতি নয়- এটি শেখার জায়গা, আত্মদর্শনের আয়না এবং জীবনকে পুনর্গঠনের আলোকশিখা।
উপন্যাসটি এগোয় সম্পর্ক, নৈতিকতা ও মানবজীবনের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। সময়ের পরিবর্তন, পারিবারিক দায়- সবকিছুর মাঝেও এহসানুল অবিচল থাকেন নিজের পথ ও নীতিতে। মানুষের জন্য কাজ করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা- এসবই হয়ে ওঠে তার জীবনের আসল ভিত্তি। যেমন মানুষ ভাঙে না- নিজেকে পুনর্গঠনের জন্য আবার জন্ম নেয় নিজের কাজে। এহসানুল হকও তেমনি একজন।
‘যেতে চাও যাও’ শুধুই প্রেমের গল্প নয়; এটি এক মানুষের গড়ে ওঠার গল্প। অতীতের অভিজ্ঞতা কীভাবে বর্তমানকে বদলে দেয় এবং একজন মানুষ কীভাবে নিজের ভেতর আলো খুঁজে পায়- উপন্যাসটি সেই রূপান্তরযাত্রার মর্মস্পর্শী বর্ণনা।
Jete Chaw Jaw - Rowshon Rube
Pre-Order
প্রবন্ধ
নাসরেদ্দিন হোজ্জা : একজন বুদ্ধিমান-বোকার গল্প – শেরজা তপন
তিনি কি একজন সুফি দার্শনিক? না কি নিছকই ভাঁড়?
তুরস্ক থেকে আজারবাইজান, ইরান থেকে চীন সব জায়গায় যার হাসির গল্পে মানুষ খুঁজে পেয়েছে গভীর প্রজ্ঞা, সেই নাসরেদ্দিন হোজ্জাকে নিয়ে এ এক বিস্ময়কর বই। বইটি পড়তে গিয়ে নতুন ধরনের পাঠ-অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়েছি।
বহু শতাব্দী ধরে হোজ্জার নামের সাথে জড়িয়ে আছে অসংখ্য কিংবদন্তী ও কাহিনি। কিন্তু আসল মানুষটা কে ছিলেন, তা জানার প্রয়াস খুব কমজনই করেছেন। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় এমন কাজ নজরে আসেনি। হয়তো এমন কাজ সমগ্র পৃথিবীতে এই প্রথম। লেখক এখানে ইতিহাস, লোকগাথা ও ধর্মদর্শনের আলোয় হোজ্জাকে পুনরাবিষ্কার করেছেন একজন চিন্তক, সমাজসচেতন ব্যঙ্গকার এবং সর্বোপরি এক অনন্য মানবপ্রেমিক হিসেবে।
বইটি পাঠককে শুধু হাসাবে না, ভাবাবে, আলোড়িত করবে। এতে আছে ইতিহাসের দলিল, সংস্কৃতির মেলবন্ধন এবং আন্দোলনের গল্প। একজন প্রজ্ঞাবান মোল্লার গল্পে আপনি খুঁজে পাবেন নিজের সমাজ, নিজের সময়, আর হয়তো নিজেকেও। প্রসঙ্গক্রমে আমরা কেউ কেউ শক্ত যুক্তি উপস্থাপন করতে বলে ফেলি তার দুএকটি গল্পও। এতদিন পরেও হোজ্জা তাই আজও প্রাসঙ্গিক দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে পৃথিবীব্যাপী।
Nasreddin Hozza : Ekjon Buddhiman Bokar Golpo - Sherza Tapon
কলমশিল্পী : স্মৃতিতে সৃজনে – মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন
ড. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন-এর লেখালেখির হাতেখড়ি স্কুলজীবন থেকে। ছোটগল্প দিয়ে সূচনা; কবিতা, বেতার নাটক হয়ে বর্তমানে প্রবন্ধ-গবেষণা-স্মৃতিকথা রচনায় নিমগ্ন। প্রায় চার দশক তিনি বাংলাদেশ বেতারে নাট্যকার, নাট্যশিল্পী, কথক ও সাহিত্যবিষয়ক অনুষ্ঠানের উপস্থাপক ছিলেন। টেলিভিশনের সাহিত্য অনুষ্ঠানেও তিনি সক্রিয়।
ড. মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে শিল্পসাহিত্যসম্পর্কিত আলোচক, প্রাবন্ধিক, স্মারকবক্তা ও সভাপতি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি বহু মনীষীর সাহচর্য পেয়েছেন। তাঁদের নিয়ে লেখেন স্মৃতিকথা আর প্রিয় সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের আলোকে রচনা করেন প্রবন্ধ। এ-সব স্মৃতিসঞ্চয় ও প্রবন্ধ নিয়েই বর্তমান গ্রন্থ- ‘কলমশিল্পী : স্মৃতিতে সৃজনে’।
Kalamshilpi : Smrityte Srijone - Mohammed Zainuddin
আমার কন্যা যেন থাকে নির্ভয়ে – উম্মে মুসলিমা
দৈনিক প্রথম আলোর উপ-সম্পাদকীয় পাতায় ২০১৫ থেকে ২০২৪ এর জানুয়ারি পর্যন্ত উম্মে মুসলিমার যেসকল আর্টিকেল ছাপা হয়েছে তার বেশিরভাগই এ বইয়ে সংকলিত। নারীর প্রতি সামাজিক বৈষম্য যেমন তাকে পীড়িত করে তেমনি কন্যাশিশুর নিরাপত্তাহীন বেড়ে ওঠা তাকে আতঙ্কিত করে। তার ‘আমার কন্যা যেন থাকে নির্ভয়ে’ প্রবন্ধের নামানুসারে এ প্রবন্ধ সংকলনের নাম রাখা হয়েছে। এ ন’দশ বছরে অনেককিছু বদলেছে তবুও সময়ের দলিল হিসেবে লেখাগুলো নতুন পাঠককেও পেছন ফিরে দেখার আগ্রহ যোগাবে বলে বিশ্বাস।
Amar Konna Jeno Thake Nirvoye by Umme Muslima
সত্তর দশকের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পশৈলী – মোজাম্মেল হক নিয়োগী
একটি জাতির কাছে স্বাধীনতার চেয়ে বেশি গৌরবের আর কিছু থাকতে পারে না এবং একই সঙ্গে বলতে হয় স্বাধীনতা অর্জন করা সহজ কোনো কাজ নয়। ইতিহাস বলে, যে কোনো দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন আত্মত্যাগের দীর্ঘ বিপ্লব ও সংগ্রামের প্রেক্ষাপট, মানুষকে সহ্য করতে হয় নির্মম নির্যাতন এবং বরণ করতে হয় মৃত্যু। ব্রিটিশদের কাছ থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতেও ধারবাহিক সংগ্রাম ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে আত্মত্যাগ করতে হয়েছে এবং সহ্য করতে হয়েছে অকথ্য নির্যাতন। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলেও ব্রিটিশদের হাত থেকে আজকের বাংলাদেশ বস্তত পাকিস্তানিদের কাছে পরাধীন ছিল। ১৯৪৮ সাল থেকে ভাষা আন্দোলনের দাবির ভিত্তিতে প্রথম সংগ্রাম ও বিপ্লবের সূত্রপাত হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনের আওয়ামী লীগের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতার বিজয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার মহাসড়ক তৈরি হয় এবং ১৯৭১ সালে রক্ষক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের প্রাণের এবং তিন লক্ষ নারীর অকথ্য নির্যাতন ও ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। এই দীর্ঘ সংগ্রাম ও স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে প্রথম রচিত উপন্যাস কোনটি? মূলত এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে সত্তর দশকের চৌদ্দ জন লেখকের মোট উনিশটি উপন্যাসের ওপর লেখা হয় প্রবন্ধগ্রন্থটি। প্রতিটি প্রবন্ধে রয়েছে লেখক পরিচিতি, কাহিনি সংক্ষেপ, নির্মাণশৈলী এবং লেখকের মতামত। আশা করা যায় পাঠকরা উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিতিসহ বিভিন্ন তথ্যাদিও জানতে পারবেন। পাঠককুল বইটি গ্রহণ করলে শ্রম সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেব।
Sattar Dashaker Muktizuddher Upannas : Bishay O Shilposhoilee by Mozammel Haque Neogi
কবির কুয়াশা – শিশির আজম
কেউই জানেনা আমার কুয়াশা আছে। বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্ত হলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা থেকে চূঁয়ে পড়া বিন্দু বিন্দু কুয়াশা। এইসব কুয়াশার আবার খিদে আছে, ক্ষোভ-বিষাদ-বিপন্নতাবোধ আছে। হ্যা, এরা আদরও চায়। তো আমার কবিতা লেখার ফাঁকে ফাঁকে এদের জন্যও জায়গা রাখবার দরকার হয়। কিন্তু এটা ভাববার দরকার নেই, কবিতায় যে অতৃপ্তি, যে শূন্যতা তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে আমার এই গদ্যকর্মের দারস্থ হওয়া। বরং আমার মনে হয়েছে একটা গদ্য লিখে শেষ করবার পর আরেকটু অন্যভাবে কবিতার কাছে ফেরা যায়। নিজেকে নতুন ভাবে কবিতার কাছে নেয়া যায়। এটা মন্দ কি! পিকাসোর যে বিপুল সংখ্যক চিত্রকর্ম, ওর ভাস্কর্যে হাত দেবার দরকার ছিল না! স্বল্প সংখ্যক ভাস্কর্য নিয়েও ওকে একজন মাস্টার স্কাল্পটরই বলা হয়। ভাস্কর্যের কারণে ওর পোন্টিংয়ের ক্ষতি হয়েছে, এ কি কেউ বলবে? কথাটা জয়নুল আবেদিনসহ অনেক সৃষ্টিশীল মানুষের ক্ষেত্রেই সত্যি। আবার অন্যভাবে বলা যায়, বিভিন্ন সময়ে বাভিন্ন পরিস্থিতিতে লেখা আমার এই গদ্যগুলো আসলে তাই যেভাবে আমি কবিতার কাছে নিজেকে নিতে চাই, আর আচমকা কবিতার কাছ থেকে অযাচিতভাবে কিছু পেয়ে যায়! এর মূল্য কি কম? এছাড়া সামাজিক জীব হিসেবে অনেক কিছু তো গায়ে এসে লাগেই! কবির একটু বেশিই লাগে। রাষ্ট্র তো বড় প্রতিষ্ঠান। পরিবারই বা নেহাত ছোট কি! সত্যিকার কবি সংখ্যালঘু। এবং সে আক্রান্ত হবেই। এটা ওর নিয়তি। তো এসবকিছুর আঁচ কোন না কোনভাবে আমার ভাবনাবিন্যাসে জায়গা পেয়েছে। মনে হয়েছে কবিতা ছাড়া অন্যভাবেও এগুলো আমি বলতে পারি।
যা হোক, প্রায় এক বছর পূর্বে ‘কবির কুয়াশা’ নামে এভাবে গদ্যের একটা পান্ডুলিপি রেডি করেছিলাম। মূলত আর্টের ওপর, অর্থাৎ সাহিত্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সিনেমা, সংগীত ইত্যকার বিষয়াদির কুয়াশা। কিন্তু এই সবকিছুর ভেতর চোরা স্রোতের মতো মিশে আছে পলিটিক্স। হ্যা, পলিটিক্স আর্টের, পলিটিক্স ইন্সটিট্যুশনের।
— শিশির আজম
০৬-১২-২০২৪
এলাংগী, কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ
Kobir Kuyasha by Shishir Azam
বিপ্লবী লীলা নাগ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ – বঙ্গ রাখাল
বঙ্গ রাখালকে সাধুবাদ ও স্বাগত জানাই। উত্তর প্রজন্মের ‘দায় ও দরদ’ পুরণে তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যের মতো কঠিন ও অপ্রশংস একটি ধারাকে বেছে নিয়েছেন বলে। কেননা, প্রবন্ধ সাহিত্য চর্চা কেবল কঠিন কাজ নয়, সৃজনশীল ও মননশীল লেখালেখির মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ। কারণ, এখানে অনেক বেশি প্রস্তুতি লাগে, অনুশীলন লাগে, অধ্যাবসায় ও অবলোকন লাগে। ফলে, তার জন্য নিজেকে প্রতিনিয়ত নিঃসঙ্গতার কাছে সঁপে দিতে হয়। দেশ, জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ, জনগণকে বুঝতে হয় তার আদ্যপান্ত সহযোগে। অনুভবে নিতে হয় তার অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরিখে। বঙ্গ সেই কঠিন পথ বেছে নিয়েছেন স্বেচ্ছায়। আমাদের প্রত্যাশা তিনি প্রবন্ধ সাহিত্যকে ঋদ্ধ করবেন, নতুন চিন্তা, নতন বয়ান হাজির সাপেক্ষে- আমাদের জন্য যোগাবেন নতুন দিশা। যে দিশার স্বপ্ন দেখেছিলেন আবুল মনসুর আহমদ, লীলা নাগ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ডা.জাফরুল্লাহ’র মতো মনীষিজন।
ড. কাজল রশীদ শাহীন
চিন্তক, সাংবাদিক ও গবেষক।
Biplobi Leela Nag O Onyanyo Prosongo by Bangl Rakhal
অণুগল্প
দর্পণ – অনুবাদ : আসাদ মিরণ মূল : এদুয়ার্দো গালেয়ানো
স্প্যানিশে Historia শব্দটি যেমন ‘ইতিহাস’ অর্থে ব্যবহৃত হয়, তেমনি ‘গল্প’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যদিও শাস্ত্রীয় বিচারে এ দুয়ের পার্থক্য সত্য ও মিথ্যার মতোই পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু লাতিন আমেরিকান লেখকরা, বিশেষ করে কথাসাহিত্যিকরাই এই দুইয়ের ভেদরেখা বা পরস্পরবিরোধিতাকে কখনো কখনো এতটাই মুছে দিয়েছেন যে তা পড়তে গিয়ে মনে হবে ইতিহাস ও গল্প যেন সহোদরা। আর এই কারণে লাতিন আমেরিকান কোনো লেখকের গল্প বা আখ্যানগুলো ইতিহাস হয়ে ওঠার শোরগোল তুলে বৈষম্যবিরোধী পাঠকের ইতিহাসপাঠের ক্ষুধা মেটায়। কিন্তু বিপরীতে ঐতিহাসিকরা ওই রকম কিছু করেছেন কখনো? করাটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু এদুয়োর্দো গালেয়ানো আসার আগে পর্যন্ত কখনোই তা ঘটতে দেখা যায়নি। গালেয়ানো মূলত ঐতিহাসিক। অসামান্য সব ইতিহাস গ্রন্থের জনক। এক একটি গ্রন্থে তিনি ইতিহাসের শিরা-উপশিরা উন্মোচন করে দেখিয়েছেন মানুষের রক্তের ক্রন্দন। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণী শক্তিতে তিনি অসামান্য এক ইতিহাসবিদ হলেও, The Mirror নামক বইটি লেখার আগে পর্যন্ত ইতিহাসের ঘটনাকে গল্পে রূপান্তরিত করার সৃজনী পরীক্ষা তিনি করেননি। বইটি একই সঙ্গে যেমন ইতিহাসের, তেমনি গল্পেরও। গল্প ও ইতিহাস এমন এক সঙ্গমে রঙিন হয়ে উঠেছে যা পাঠবিমুখ পাঠককেও উজ্জীবিত করে তোলে। এই গ্রন্থের আরও একটি বড় আকর্ষণ এর বৈশ্বিক পরিসর আর সর্বজনীনতা, কিন্তু গালেয়ানোর শৈল্পিক মিতভাষিতায় তা হয়ে উঠেছে বহনযোগ্য এক দর্পণের মতো, যেখানে যেকোনো কাল, যেকোনো জাতি, এমনকি ইতিহাস-বঞ্চিত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিও তার নিজের চেহারা দেখে নিজেকে চিনে নিতে পারবে। এটি এমনই এক দর্পণ যেখানে পৃথিবীর অন্য সব মহাদেশের মতো আমাদের এই উপমহাদেশ, এমনকি রাজধানী ঢাকাসহ বাংলাদেশের ঘটনাও প্রতিফলিত হয়েছে ঐতিহাসিক নিষ্ঠায় আর সাহিত্যিক সুজনশীলতায়। অমূল্য হীরকখণ্ডের এই লোভনীয় ভার পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছেন বিশ্বস্ত বাংলা তর্জমায় আসাদ মিরণ।
Dorpon (Mirror) by Eduardo Galeano. Translated by Asad Miron
রুখসানা কাজলের অণুগল্প
‘জল পড়ে, পাতা নড়ে’। ‘পাতা নড়ে’ এর স্পন্দনটা যদি এখানেই শেষ হয়ে যেত তাহলে কোনো কথাই ছিল না। আসলে তো ঝরেপড়া জলবিন্দু পাতার সাথে আমাদের অন্তরাত্মাকে নাড়াতে নাড়াতে নিয়ে যায় সমুদ্র থেকে মহাসমুদ্রে। অণুগল্প সে-রকমই কিছু।
রুখসানা কাজলের অণুগল্প
গরু চোর
গরুচোর
সেদিন এক গরুচোরের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল সবার, চোরটি নিজে থেকেই বলল—আমার নাম মজিদ। আমি একটা গরুচোর।
দলে নিয়োগ চলছিল। ইন্টার ডিস্ট্রিক বাস ডাকাতদলের সভাপতি জুম্মন খাঁ, অজ্ঞানপার্টি অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি, নিখিলবাংলা পকেটমার মহাসঙ্ঘের সেক্রেটারি বসা। এরাই দলের নিয়োগদাতা।
কিন্তু মজিদকে দেখে মোটেও গরুচোরের মতো লাগছিল না। গরুচোর হবে গরুচোরের মতো কিন্তু এরে সে রকম লাগছে না। এরে মকবুলের মতো লাগে।
মকবুল কে? মকবুল হলো মুরগি চোর। একসময় এই দলের হয়ে কাজ করত। এখন দল ভেঙে আলাদা দল করেছে। টেক্কা দিতে চায়।
অজ্ঞান স্পেশালিস্ট একাব্বর আলি সরু চোখে মজিদের দিকে তাকাল। তার ইচ্ছে করছে চোখেমুখে মলম ঘষে দিতে। একরাশ সন্দেহ নিয়ে বলল—তা মজিদ মিয়া, কয়টা গরু তুমি চুরি করছ?
মজিদ মাথা চুলকায়। ঘাড় চুলকায়। একটু লজ্জাও পায়। বলল—খুব বেশি না ওস্তাদ, আমি তো রেনডম গরু চুরি করি না। যখন কোরবানি আসে, গরুর হাটে ঘোরাঘুরি করে চান্সে চুরি করি। বছরে ওই একটাই সিজন আমার।
—তাই বল! একাব্বর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সন্দেহ আমার ঠিকই ছিল—ভাবতে ভাবতে সবার দিকে তাকিয়ে একটু ফুলে ওঠে, গর্বে। আসলে এই ব্যাটাকে মুরগি চোরের মতো লাগছিল। বিশ্বাসঘাতক মকবুলের চেহারার লগে মিল আছে। মকবুলও ছিল বিরাট মুরগি চোর।
—তা এইখানে কি মনে করে?
মজিদ বলল—ওস্তাদ, আমারে দলে নেন। চুরিধারী দল থেকে না করলে পোষায় না। একলা একলা ভালো লাগে না। মামারা ধরলে ছাড়ানোর কেউ থাকে না কোর্টে চালান খাইয়া যাই।
মজিদের কথায় সিদ্ধান্তের জন্যে সেক্রেটারি তাকায় সহ-সভাপতির দিকে, সহ-সভাপতি তাকায় সভাপতির দিকে। সভাপতি কারো দিকে না তাকিয়ে নিজের ডানহাতের চার আঙুলে পরা আংটির দিকে তাকিয়ে রইল। দুর্লভ পাথর বসানো সব আংটি। কোনোটি হীরা। ইয়াকুত আর লাল জমরুদ পাথরের আংটি দুটি নাকি খুবই বিখ্যাত। সাদা চুনি নাকি পৃথিবীর কোথাও নেই। একটিই। তাও জুম্মনের হাতে, ভাবা যায়! এই আংটিগুলির বৈশিষ্ট্য হলো ডান হাতে পরতে হয়। কিন্তু জুম্মনের হাতে মোট আঙুল চারটি। একবার ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহস্থের দায়ের কোপে একটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। ফলে চার আঙুলেই আংটি পরতে হয়।
কাটা আঙুলের দিকে তাকিয়ে জুম্মন ডাকাত হতাশায় মাথা নাড়ে—মজিদ, গরুচোর মুরগি চোরের বিষয় না, আমরা এমন এক হাত সাফাইয়ের খোঁজ করছি, যে মুরগি নয়—মুরগির পিত্তথলি হাত চালিয়ে বাইরে আনতে পারবে, কিন্তু মুরগি টের পাবে না। পারবে?
ওস্তাদের কথায় খুব হতাশ হয়ে গেল গরুচোর মজিদ। চোখেমুখে পানি চলে এলো প্রায়। এত সুক্ষ্ম কাজ পারবে না সে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—খুব ইচ্ছা ছিল আপনাদের সাথে কাজ করার। হলো না। বিদায় দেন ওস্তাদ।
বলে সবার সাথে হাত মিলিয়ে মজিদ চলে গেলে জুম্মন খাঁ নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল—আমার আংটি, আমার আংটি!
…………
মকবুলের ডেরায় যখন মজিদ চারটি আংটি ছড়িয়ে দিল তখন খুব হাসাহাসি হলো, জুম্মন ওস্তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে কল্পনা করে। হাত সাফাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেল মজিদ।
মকবুল কথা দিলে কথা রাখে।
গরুচোর
কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা
কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা
গ্রামের পাশে যে বিশাল বাদাম ক্ষেত আর ক্ষেতের পাশে যে ছোট নদী, সে নদীতে মাঝারি সব ঢেউ ওপার থেকে এপাড়ে আসে খড়কুটো মুখে নিয়ে। আর কত কিছু ভেসে আসে আর চলেও যায়—সারা দিনভর ছোটনেরা সেইসব দেখে পাড়ে বসে বসে।
ছোটনেরা মানে হলো—হাবিবুল, রতন, মোবারক, শেফালি বকুল এরা। কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা। তারা প্রতিদিন নদীতে আসে আর কাঁচা বাদাম খেতে খেতে লক্ষ করে নদীটাকে। নদীর ভেতরে কত কিছু। কাদাখোঁচা একটি দুটি। বালিয়া হাঁসের সাদা পাখনা উড়তে থাকে। আর ওপারের মেঘ যখন উড়তে উড়তে এপারে আসে তখন জলিল কাকার সময় হয় জোয়ালের গাই দুটাকে গোসল দেয়ার। গাই দুটার গোসল দেখতে দেখতে আর বাদাম খেতে খেতে দলের মধ্যে মোবারক নামে যে আছে, সে একটা প্রস্তাব দিল। প্রস্তাব দেয়ার আগে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব নিয়ে কয়েকটা জানাশোনা তথ্যও দিল। যেমন—এই নদীতে কিছুই ডোবে না।

বাকিরা মাথা নাড়ে—হুম।
গরু ডোবে না, খড় ডোবে না। নাও-লঞ্চ কিছুই ডোবে না। ভেলা ডোবে না।
সবাই মাথা নাড়ে। কাঁচা বাদাম খায়।
—চল আজকে একটা খেলা খেলি। মিনুরে ডুবাই দেই। দেখি ডোবে কি না?
ছোটনরা একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। প্রস্তাবে জোর সমর্থন দেয় নুরু। প্রস্তাব সমর্থন নিয়ে নুরু কারো দিকে তাকায় না। নদীর পেটে জলের প্রবাহ দেখতে দেখতে তারা স্কুলঘর দেখে। দূরের আকাশছোঁয়া মিনার মসজিদ দেখে।
—মিনুও ডুবত না। এই নদীতে কিছুই ডোবে না–বলে সাহস দেয় নুরু। ততক্ষণে মিনুকে নিয়ে এসেছে মোবারক।
মিনু জল দেখে ভয় পায়। বলে—মিঁউ!
বিশাল নদী। বিশাল চর। মিনু ভয় পায়। ডাকাডাকি শুরু করে দেয়—মিঁউ মিঁউ।
মিনুকে কোলে নেয় হাবিবুল। হাবিবুল থেকে নেয় রতন। রতন থেকে নেয় শেফালি। শেফালি থেকে নেয় রাজন। রাজন থেকে নেয়া নুরু। নুরু থেকে কেউ নেয় না। কারণ নুরু কাউকে দেয় না। সে মিনুকে ছুড়ে দেয় নদীতে।
সবাই হাসে। মিনু সাঁতার কাটে। ঠিকমতো পারে না। নদীতে ঢেউ। তলিয়ে যায়। ছোট্ট মাথা। ডোবে ভাসে। সবাই হাসে–খুশিতে হাততালি দেয়।
দুই ঢেউয়ের চাপে পড়ে মিনু ডাকে—মিঁউ মিঁউ।
প্রাণপণ চেষ্টা করে মিনু কচি পা দিয়ে পাড়ে আসতে পারে না। দূরে সরে যায়। আবার আসে। পাড়ের কাছে আসেও। কিন্তু নুরুরা ঢিল ছোড়ে। হি হি করে হাসে। হাত তালি দেয়।
মিঁউ মিঁউ করতে করতে নদীর ভেতরে চলে যায় মিনু। ঢেউয়ের ভাঁজের ভেতরে চলে যায়। ডুবে যায়। পাড়ে বসে রাজন শিস দেয়।
…………
রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরো ব্যাপারটা আবার দেখে ছোটন। মিনু ডুবে যাচ্ছে। ভেসে উঠছে। চিৎকার করে ওঠে ছোটন। ঘামে নেয়ে ওঠে সে। কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না। ঘুমের মধ্যেই ছোটন বোঝে ঘুম না ভাঙলে সে নদী থেকে আর মিনুকে উঠাতে পারবে না।
সকালবেলা তাড়াতাড়ি মিনু যে কাজটি করে তা হলো ছোটনের বাবা-মাকে নিয়ে নদীর পাড় চলে এলো। তারা দেখল—নদীর ভেতরে একটা লাল জামা ভাসছে ছোটনের।
২৪১৯
কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা
জোড়া নারিকেল বাড়ি
হাতেগোনা যে-ক’জন লেখক অণুগল্পের ভিত্তি গাড়তে কিংবা প্রচার প্রসার করার মাধ্যমে প্রথম দশকেই একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন কিংবা বলা যায়, অণুগল্পের বিভিন্ন ধরন এবং ধারণায় সাহিত্যের এ-মাধ্যমটি বর্তমানে বহুচর্চার ফল্গুধারায় দুইবাংলার পার ছাপিয়ে গেছে বটে, আশার কথা হচ্ছে, কামরুজ্জামান কাজল বিশুদ্ধ অণুগল্পের ধারক-বাহক হয়েই পাঠকমহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্ববর্তী ৩টি গ্রন্থে আমরা তা-ই দেখেছি। আর এখানেই প্রকৃত অণুগল্প আর কাজল সমার্থক হয়ে উঠেছেন।
‘জোড়া নারিকেল বাড়ি’ লেখকের চতুর্থ অণুগল্পের বই। বইটির সাফল্য কামনা করি।
-বিলাল হোসেন
জোড়া নারিকেল বাড়ি
রোজনামচা
রোজনামচা বা দিনলিপি কেন পড়ে মানুষ? কী দরকারে আসে এই দিনপঞ্জীপাঠ? স্যামুয়েল পেপিস (১৬৩৩-১৭০৩) কেন বিখ্যাত হয়ে গেলেন কেবলমাত্র ডায়েরি লিখে? কেননা তাঁর ডায়েরি তৎকালীন লন্ডনে (১৬৬৫) ছড়িয়ে পড়া মহামারী প্লেগ ও চারদিন (২রা-৬ই সেপ্টেম্বর, ১৬৬৬) ধরে চলা লন্ডন শহরকে পুড়িয়ে খাক করে দেওয়া বিধ্বংসী অগ্নিকা-ের অনুপুঙ্খ বিবরণ তাঁর ডায়েরিতে ধরেছেন পেপিস। যা আজ ইতিহাসের মর্যাদা পেয়েছে। কিংবা ধরুন, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি’-র ‘নোটবুক’ বা পাবলো নেরুদার ‘মেমোয়্যার্স’ আমাদের কাছে আকর্ষণীয় কেন? না, যে যুগ আমরা পেরিয়ে এসেছি আর কোনোদিন যাওয়া যাবে না সেখানে, দিনপঞ্জী আমাদের নিয়ে যায় সে মুহূর্তক্ষণে! চিলেকোঠায় অথবা বহুদিন বন্ধ থাকা তোরঙ্গের গর্ভান্ধকার থেকে খুঁজে পাওয়া কোনো ডায়েরি এক অপরিসীম আনন্দে মন ভরায়, দেয় আবিষ্কারের আনন্দ-মূর্ছনা!
রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’-র যে অংশে কবি নানান মানুষের স্নান করার দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন, সে ছবি রচনার মধ্যে সেই পুরোনো কলকাতার যে স্কেচ উঠে আসে, তা আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, অথচ কী আশ্চর্য চিত্রময় লিপ্যাঙ্কন। মনের ভেতর ছবি হয়ে বেঁচে আছে শতাব্দী পেরিয়ে। এও তো সেই রোজনামচাই! কবিগুরুর অজস্র চিঠিতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য তাৎক্ষণিকতা, ‘হে ক্ষণিকের অতিথি’ হিসেবে নানান দৃশ্যকল্প, ছবি সে-ও সেই দিনপঞ্জীর কথাই মনে করায়। পুরোনো দিন, পুরোনো সম্পর্ক সবই ধরা থাকে প্রকৃত শিল্পীর কলমে। সে কারণেই একজন শক্তিমান লেখকের লেখা রোজনামচা বা দিনলিপি আমাদের সাগ্রহবস্তু। যে দিন চলে গেছে, যাকে ধরে রাখতে পারিনি, সে সন্ধানে ডুব দিতে পারি ইচ্ছে করলেই। মনে করতে পারি, ‘বন্ধু কী খবর বল, কতদিন দেখা হয়নি!’
এ-কারণেই ‘রোজনামচা’-র বহুল প্রচার আশা করি।
সিদ্ধার্থ দত্ত
৮.১০.১৮
রোজনামচা
কবিতা
মায়াবী ট্রেন – মৃন্ময় মনির
ভ্রমণ অনির্দিষ্ট। জন্ম থেকেই তার শুরু। মানুষের ক্ষেত্রে সাধারণত একশো বছরের ভেতরেই তা ঘোরাফেরা করে! বেড়ানোর জন্য অনেক যন্ত্রযান রয়েছে কিন্তু ট্রেনের মতো এমন মায়াবী ভ্রমণ আপনি কোথাও পাবেন না! অবশ্য আপনি বসে থাকলেও আপনার পথচলা একদিন শেষ হবেই, প্রাণীর জন্য দ্বিতীয় কোনো পথ এখনো খোলা নেই।
Mayabi Train - Mrinmay Monir
নির্মোহ পৃথিবীর কথা – আব্দুল্লাহ্ জামিল
নির্মোহ পৃথিবীর কথা, নামের মধ্যে একধরনের সত্যের অহংকার এবং সাহসের স্বচ্ছরূপ দেখতে পাওয়া যায়। নামকরণ কবির একটি গ্রন্থের তাৎপর্যপূর্ণ সংযুক্তি। হঠাৎ কখনো নামকরণের সঙ্গে বইয়ের বিষয়ের কোনো মিল থাকে না। তবে নামকরণ যে লেখকের সুচিন্তিত একটি অধ্যায়, তা লেখকমাত্র জানেন। আব্দুল্লাহ জামিল একজন স্থিরমগ্ন কবি। তিনি চিকিৎসা পেশার ব্যস্ততার কারণে, খুব বেশি লিখতে পারেন না। তবে, খুব যে কম লেখেন তাও নয়। বর্তমান ‘নির্মোহ পৃথিবীর কথা’ কাব্যগ্রন্থে তিনি কখনো নস্টালজিক, কখনো প্রকৃতিপ্রেমিক, কখনো প্রতিবাদী, কখনো কোমল। তবে তার প্রতিটি উচ্চারণই অকপট, সরল ও সাবলীল। এটি কবিতার একটি অনমনীয় গুণ। ছন্দসচেতনতা তার কবিতাকে আভিজাত্য এনে দিয়েছে। প্রাজ্ঞতা দিয়েছে। তিনি কথা বলার ঢঙে কবিতা লিখে চলেন, তবে তার লেখা বলার চেয়ে অলংকৃৃত। বইয়ের কবিতাগুলোতে কোথাও কোনো ঝুলে পড়া বা মেদস্বর্বস্ব অতিকথন নেই। টানটান সাবলীলতায় তিনি একবার প্রেম আর একবার বিষাদের সংগীত শোনান। তবে তার কবিতার সময় ও মৃত্যুচেতনার বিষয়টি গভীর তাৎপর্য বহন করে। প্রিয়জনের কাছ থেকে অবহেলা, প্রত্যাখানের মতো অনাকাক্সিক্ষত বিষাদও তার কবিতার অন্যতম সমাপ্তি। কবির নির্বাচিত শব্দ আর আর অলংকৃত বিন্যাস, তাকে পরিণতি দিয়েছে। শব্দ ও বাক্যের পরিমিতি বোধ ও আবেগের নিয়ন্ত্রণ তার কবিতার নিটোল চারিত্র।
-ওবায়েদ আকাশ
কবি ও সাংবাদিক
Nirmoho Prithibir Katha - Abdullah Jamil
অন্য করিডোরের ফুল – কাদের পলাশ
ধোঁয়াটে ‘আত্মা’ থেকে নয়, বরং কবিতা তার অন্তর্বলয়ের মোক্ষম ভাষাটি খুঁজে পায় কেবলই বোধসামুদ্রিক শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রবাহের স্বতঃস্ফূর্তি থেকে, কবির তিনটি চোখের সম্মিলিত পর্যবেক্ষণের সারাৎসার হয়ে যা একাধারে দৃশ্যমানতা ও অদৃশ্যমানতাকে ধারণ করে তার একান্ত নিজস্ব নিপুণ কৌশলে, দৃশ্যত কখনো যা আটপৌরে বসন পরা, কখনো আবার গা-ভর্তি অলংকারের চোখ ঝলসানো সাজগোজে।
কবি কাদের পলাশের ‘অন্য করিডোরের ফুল’ সংকলনটি এমনই একজোড়া ও অনুসন্ধানী চোখের নজরকাড়া ভিন্ন ভিন্ন ৪২টি কথালিপি, যেখানে বোধের পারম্পর্য বজায় রেখে শব্দের স্বতঃস্ফূর্ত সীবনে কবিতার আত্মভাষার রচন।
এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত অধিকাংশ কবিতার সহজ-কথার কথায় অনেক চিত্রকল্প, অনেক তির্যকে অনেক ইঙ্গিত। সেসবের সবকিছুই বিষাদ-কবিতা হয়ে ওঠার শর্তবহ। ছত্রে ছত্রে নরত্বারোপের কুশলী সীবন এই কবির কবিতায় এক ভিন্ন ধরনের আলাপচারিতার মাত্রা আরোপ করে বৈকি! কবি কাদের পলাশ তাই বর্তমানের মাটিতে দাঁড়িয়েও ইতিহাসকে নিয়ে আসতে পারেন অতি অনায়াসে তাঁর কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবনার অনুসারী করে। তিনি একজন সু-সাংবাদিক দর্শকমাত্র নন, নিবিড় পর্যবেক্ষক আগাপাশতলা। তাঁর নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের হাত ধরেই ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখা কাগজের কলামে কলামে।
আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কবি কাদের পলাশের অন্য করিডোরের ফুল কাব্যগ্রন্থখানি সংবেদনশীল পাঠকের কাছে গভীরতর জীবনবোধের অনবদ্য কিছু উপাদান জুগিয়ে অকৃত্রিম মান্যতা কুড়োবে অনায়াসে।
-সুভাষ সরকার
Anyo Corridorer Ful - Kader Palash
দুঃখ নদীর ধারাপাত – আদ্যনাথ ঘোষ
কাব্যস্বরের নিজস্বতা একজন কবির জন্য বড়ো বেশি প্রয়োজন। আদ্যনাথ ঘোষ কবিতায় সেই চিরায়ত কাব্যস্বরের পরিবর্তন ঘটিয়ে আলাদা ইমেজ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস, প্রতিমা ব্যবহারে পাঠকচিত্তে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন। শব্দ ও চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে আদ্যনাথ ঘোষের কবিতার স্বতন্ত্রধারা পরিলক্ষিত হয়। কবিতার শরীরসজ্জা গদ্যাত্মক হলেও আদ্যনাথ ঘোষের কবিতা আত্মাকেই ধারণ করে। তাঁর কবিতার শিল্পভাষা, কল্পনার উচ্ছ্বাস, কাব্যিক ঢং অন্যান্য কবিদের থেকে অনেকটাই আলাদা। আদ্যনাথ ঘোষ মূলত স্বতন্ত্রস্বরের রূপকাশ্রয়ী লিরিকধর্মী ও ব্যঞ্জনাধর্মী কবি। কবিতার ভেতরে ঘোর, আত্মমগ্নতা ও পরাবাস্তবতা নির্মাণে ঈর্ষণীয় কারিগর। ইমেজের ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় এ-কবিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রে উন্নীত করেছে। তাঁর কবিতার আত্মা কাব্যপাঠকচিত্তে আলাদা অনুরণন সৃষ্টি করে। উত্তরাধুনিক যুগের এ-কবির কবিতার বাঁকবদল সত্যিই অনন্য।
প্রকাশক
Dukkho Nodir Dharapat - Adyanath Ghosh
অতলের পদ্মপুরাণ – লীনা ফেরদৌস
‘সহজ কথা যায় না বলা সহজে- রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন। সহজ কথা আসলে বুদ্ধিবৃত্তিক আর সংবেদনার ভাষা, দর্শনের একরকম উন্মোচনই তো!
লীনা ফেরদৌস কবি এবং তার এই কবিতাগুলোর ভেতর শৈশবস্মৃতি, একাকীত্ব, নৈঃসঙ্গ্য-স্বরূপ আর দেশ-ভাবনা ডুব-সাঁতারের মতোই পাঠকের কাছে ধরা দেয়।
‘নদী আসলে নরম নয়-অভিমানের স্রোতে সব ভাসায়।‘
কিংবা-
‘নারীরাই হয়তো নীল আকাশ, প্রতিটি মেঘে লুকিয়ে আছে একটি অপেক্ষমান জন্ম।’
দুটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে লীনার এর আগে, এটি তৃতীয় বই-সম্ভাবনার একরাশ পাপড়ি ছড়ানো লীনার কবিতা। বইটির পাঠক-মনোযোগ আকৃষ্ট হোক প্রভূত পরিমাণে-এই প্রত্যাশা করাই যায় অনায়াসে।
Ataler Padmapuran - Lina Ferdows
হাসপাতালের বারান্দা – আতিকুর রহমান হিমু
 হাসপাতালের বারান্দা।
হাসপাতালের বারান্দা।
ক্যান্সারাক্রান্ত বাবার পাশে বিষণ্ন মা বসে আছেন।
কেমোথেরাপি চলছে; তখন ছোটোভাই বাঁধন বিদেশে, আমি অনেক দূরের শহরে কর্মসূত্রে, কখনো-বা ফিরি উৎকণ্ঠিত পথ পেরিয়ে মধ্যরাতের ক্লান্তি নিয়ে; এইসব লেখা লিখিয়ে নিয়েছে একটা অসুখমুখর সময়। অধিকাংশই ২০২২-২৩ সময়ের। তারপরে সে-বার (কবি মালেকা
ফেরদৌস) আপার সাথে, ২০২৪-এ তনুশ্রীকে নিয়ে হাসপাতালে কুঁড়িয়ে পাওয়া শব্দগুচ্ছ টুকে রেখেছিলাম। কবিতার হয়ে উঠলো কি না! সংশয়…
Haspataler Baranda by Atiqur Rahaman Himu
উপন্যাস
যেতে চাও যাও – রওশন রুবী
‘যেতে চাও যাও’- ভালোবাসা, জীবনসংগ্রাম এবং মানুষের অন্তরযাত্রা নিয়ে রচিত এক শক্তিশালী উপন্যাস। এহসানুল হক একজন নীতিবান, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল মানুষ। ছোটবেলা থেকেই তার ভেতরে আছে সততা, সহমর্মিতা ও অন্যের পাশে দাঁড়ানোর সহজাত মন।
জীবনের পথে তিনি দেখেছেন ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং মানুষের বহুমুখী রূপ। তবু তিনি নিজের নৈতিক অবস্থান থেকে কখনো সরে যাননি।
এক সময় গভীর ব্যক্তিগত ক্ষত তাকে ভেঙে দেয়, কিন্তু সে ভাঙন থেকেই এহসানুল নতুনভাবে নিজেকে গড়ে তোলেন। হারানোর বেদনাকে শক্তিতে পরিণত করেন; জীবনজয়ের আকাঙ্ক্ষা তাকে উদ্দীপ্ত করে, আর ব্যর্থতা তাকে পথ দেখায়। তার কাছে ভালোবাসা শুধু অনুভূতি নয়- এটি শেখার জায়গা, আত্মদর্শনের আয়না এবং জীবনকে পুনর্গঠনের আলোকশিখা।
উপন্যাসটি এগোয় সম্পর্ক, নৈতিকতা ও মানবজীবনের অন্তর্গত দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। সময়ের পরিবর্তন, পারিবারিক দায়- সবকিছুর মাঝেও এহসানুল অবিচল থাকেন নিজের পথ ও নীতিতে। মানুষের জন্য কাজ করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা- এসবই হয়ে ওঠে তার জীবনের আসল ভিত্তি। যেমন মানুষ ভাঙে না- নিজেকে পুনর্গঠনের জন্য আবার জন্ম নেয় নিজের কাজে। এহসানুল হকও তেমনি একজন।
‘যেতে চাও যাও’ শুধুই প্রেমের গল্প নয়; এটি এক মানুষের গড়ে ওঠার গল্প। অতীতের অভিজ্ঞতা কীভাবে বর্তমানকে বদলে দেয় এবং একজন মানুষ কীভাবে নিজের ভেতর আলো খুঁজে পায়- উপন্যাসটি সেই রূপান্তরযাত্রার মর্মস্পর্শী বর্ণনা।
Jete Chaw Jaw - Rowshon Rube
আমি চরিত্রহীন হতে চাই – সাইয়িদ রফিকুল হক
এটা একজন সামাজিক প্রতিবাদী মানুষের অভিজ্ঞান। সমাজের অন্যায় দেখতে-দেখতে মানুষ যখন একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, আর চারিদিকে দেখতে পায় নীতিভ্রষ্ট ও চরিত্রহীনদের দাপট, তখন মানুষের ভেতরে বাড়তে থাকে ক্ষোভের আগুন। একজন শাকেরের তখনই মনে হয়েছে, এরচেয়ে বুঝি চরিত্রহীন হওয়াটাই ভালো। তাই, সে একসময় বিদ্রোহীর প্রতিমূর্তি হয়ে সরোষে বলে উঠেছে—আমি চরিত্রহীন হতে চাই। পরে অবশ্য সে শান্তচিত্তে ভেবে দেখেছে, সে চরিত্রবানই থাকতে চায়। আর সে চরিত্রবান থেকেই দুনিয়ার সর্বস্তরের চরিত্রহীনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়। এই তার মনোবাসনা।এটা একজন প্রতিবাদী শাকেরের গল্প। ‘আমি চরিত্রহীন হতে চাই’মানে চরিত্রহীন হওয়া নয়, একটা জলন্ত প্রতিবাদ। একটা বিদ্রোহ। আর সমাজ-রাষ্ট্রের যাবতীয় দুষ্কর্ম, অনাচার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর এক জলন্ত উদাহরণ।
শাকেরের দ্রোহ, ক্ষোভ আর সাহসিকতার এই উচ্চারণ সববয়সি পাঠকের ভালো লাগবে বলে আশা করছি।
Ami Charitrahin Hote Chai
রোড টু পামির : ইতিহাস ও আদিম প্রকৃতি যেখানে মিশেছে – এলিজা বিনতে এলাহী
ভ্রমণ তাঁর নেশা। বেরিয়ে পড়েন যখন-তখন। কখনও সপরিবারে, কখনও সবান্ধব, কখনও শুধু নিজের সঙ্গে। তাঁর আকর্ষণের বিষয় ইতিহাস। সম্প্রতি ভ্রমণ করে ফিরেছেন পৃথিবীর ছাদখ্যাত পামির মালভূমির এমাথা-ওমাথা।
মধ্যএশিয়ার দেশ তাজিকিস্থানের পামির মালভূমির পুরো অঞ্চলটির নাম গর্নো-বাদাখশান প্রদেশ। স্থানীয়রা বলেন পামির হাইওয়ে। যুগে যুগে বণিক, তীর্থযাত্রী, রাজবন্দি, প্রত্নসন্ধানী অভিযাত্রীদলের রেশমপথ। তাজিকিস্থানের ৪৫ ভাগ স্থান জুড়ে রয়েছে এই পাহাড়ি অঞ্চল। ১০ দিনের রোড ট্রিপে তিনি ভ্রমণ করেছেন তাজিকিস্থানের ৪টি ঐতিহাসিক শহর আর পামির মালভূমির ৪টি জেলা। তাছাড়াও এই রোড ট্রিপে কত ছোটো-ছোটো শহর, গ্রাম, পার্বত্য অঞ্চল ছুঁয়ে গেছেন, খানিক থেমেছেন তার ইয়ত্তা নেই।
তাজিকিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস, পামির মালভূমির আদিম প্রকৃতি, প্রাচীন বণিকদের রেশমপথ, মানুষ, সংস্কৃতি, খ্যাদাভাস, জীবন- সব মিলেমিশে বাংলাদেশি ভ্রমণকারী এলিজা বিনতে এলাহী রচনা করেছেন মধ্যএশিয়ার প্রাচীন রাজপথ ভ্রমণের এক আকরগ্রন্থ ‘রোড টু পামির’।
Rode To Pamir : Itihas O Adim Prokriti Jekhane Misheche - Eliza Binte Elahi
জিনকন্যা নার্গিসের প্রেম (দ্বিতীয় সংস্করণ) – হুমায়ুন কবির
সম্মানিত পাঠক, আপনি যতই উপন্যাসের মর্মমূলে প্রবেশ করবেন, ততই সবিস্ময়ে আবিস্কার করবেন, এটি একটি অবিশ্বাস্য প্রেমকাহিনী। এই প্রেম নিছক মানবীয় নয়, এই প্রেম মানুষ ও জি¦নকন্যার। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘ক্রস-অ্যাফেয়ার’। উপন্যাসের নায়ক নাসির এক শ্বাসরুদ্ধকর মহাজাগতিক ভ্রমণে পাঠককে নিয়ে গেছেন সুগভীর রোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চারে। মানবজীবনের গতিপথ শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্যের কালচক্রে বাঁধা হলেও এ উপন্যাসের জীবনচক্র যেন আবর্তিত হয়েছে উল্টোরথে।
এই উপন্যাসের লেখক শুধু জীবনকেই স্পর্শ করেননি, তিনি স্পর্শ করেছেন ভূগোল ও ইতিহাসকেও। তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে বিশ্বের দর্শনীয় স্থান, ঐতিহাসিক নিদর্শন, জি¦নজাতির ইতিহাস, সমাজ, সংসার ও প্রেম। উপন্যাসের বাঁকে বাঁকে পাঠক আন্দোলিত হবেন মানবজীবনের হাসিকান্না, স্বপ্ন, অশ্রু, দুঃখ, অভিমান, হিংসা, ঘৃণা, প্রতীক্ষা ও বিসর্জনের দোলাচলে।
-ড. শাহেদ ইকবাল
Jinkonna Nargiser Prem - Humayun Kabir
তোমার চোখের জলে আমার জন্ম, মা – সারাবান তহুরা মৌমিতা
 মায়ের চোখের জল শুধু দুঃখের নয়, তা ভালোবাসার, ত্যাগের আর সীমাহীন আশ্রয়ের প্রতীক। ‘তোমার চোখের জলে আমার জন্ম, মা’ গ্রন্থটি মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে লেখা গভীর আবেগময় রচনা। এখানে উঠে এসেছে সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা, অশ্রুর ভেতরে লুকিয়ে থাকা শক্তি আর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সন্তানের জন্য মায়ের অগাধ আত্মত্যাগ।
মায়ের চোখের জল শুধু দুঃখের নয়, তা ভালোবাসার, ত্যাগের আর সীমাহীন আশ্রয়ের প্রতীক। ‘তোমার চোখের জলে আমার জন্ম, মা’ গ্রন্থটি মাতৃত্বকে কেন্দ্র করে লেখা গভীর আবেগময় রচনা। এখানে উঠে এসেছে সন্তানের প্রতি মায়ের মমতা, অশ্রুর ভেতরে লুকিয়ে থাকা শক্তি আর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সন্তানের জন্য মায়ের অগাধ আত্মত্যাগ।
এই উপন্যাসটি আমার মাকে কেন্দ্র করে লেখা একটি হৃদয়স্পর্শী গ্রন্থ। মায়ের অশ্রু, হাসি, ত্যাগ আর ভালোবাসা সবই আমাকে গড়ে তুলেছে আজকের আমি হিসেবে। এই বইয়ে আমি ফিরে গেছি মায়ের সাথে কাটানো স্মৃতি, সংগ্রাম আর অনন্ত মমতার গল্পে।
এই বই শুধু একটি সাহিত্যকর্ম নয়, এটি প্রতিটি পাঠকের হৃদয়ে স্পর্শ করবে, মনে করিয়ে দেবে আমাদের জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের পেছনে আছে মায়ের অশ্রু, প্রার্থনা ও অমলিন ভালোবাসা।
এই বই শুধু আমার ব্যক্তিগত অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ নয়, এটি প্রতিটি মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধায় এক বিনম্র উপসর্গ।
Tomar Cokher Jole Amar Jonmo, Ma - Saraban Tahura Moumita
নক্ষত্রের চোখে জল – আতাউর রেজা পরশ
 শ্রাবণ মাসের শেষ দিক। আকাশে সাদা মেঘ উড়ে বেড়ায়। রাতদিন ঝরঝর করে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির অশান্ত গতিপ্রকৃতিকে নিস্তব্ধ করে দেয়। বাইরে কেবল জলের হা হুতাশী ক্রন্দন শুনতে পাই। বৃষ্টি আমাকে ঘরের মাঝে বন্দি করে রাখে। একা একা আমি বসে জলের খেলা দেখি। আমার আস্তাহারা মন কেন যেন বারবার কেঁদে ওঠে। সে যেন কার শূন্যতা অনুভব করে। প্রকৃতি জলের ছোয়ায় সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার মনটা সতেজ হয় না। মন তো কেবল ভালোবাসায় সতেজ হয়। আর সেই ভালোবাসার সন্ধানেই আমি নক্ষত্রের চোখে জল লিখলাম।
শ্রাবণ মাসের শেষ দিক। আকাশে সাদা মেঘ উড়ে বেড়ায়। রাতদিন ঝরঝর করে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টির অশান্ত গতিপ্রকৃতিকে নিস্তব্ধ করে দেয়। বাইরে কেবল জলের হা হুতাশী ক্রন্দন শুনতে পাই। বৃষ্টি আমাকে ঘরের মাঝে বন্দি করে রাখে। একা একা আমি বসে জলের খেলা দেখি। আমার আস্তাহারা মন কেন যেন বারবার কেঁদে ওঠে। সে যেন কার শূন্যতা অনুভব করে। প্রকৃতি জলের ছোয়ায় সজীব হয়ে ওঠে। কিন্তু আমার মনটা সতেজ হয় না। মন তো কেবল ভালোবাসায় সতেজ হয়। আর সেই ভালোবাসার সন্ধানেই আমি নক্ষত্রের চোখে জল লিখলাম।
Nokkhotrer Chokhe Jol - Ataur Reza Porosh
পেপার ব্যাক
সিমান্তিনী
ভূমিকা
‘সীমান্তিনী’ আমার লেখা দীর্ঘ কবিতার মধ্যে অন্যতম। বারোটি কবিতা নিয়ে এই বইটি। কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে প্রেমের পাশাপাশি পাহাড়ি সৌন্দর্য, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী গারো, হাজং প্রভৃতি আদিবাসীদের সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও তাদের জীবনধারা। পাহাড়ি নারীর সৌন্দর্য, বালুকণা, সমুদ্র, আঁকাবাঁকা-উঁচুনিচু পথের দৃশ্যও এই বইতে চিত্রিত হয়েছে। প্রতিটি কবিতার পাতা রাঙানো হয়েছে ভালোবাসার রঙে।
কিসিঞ্জার ভূঁইয়া
০১ সেপ্টেম্বর, ২০২০
সীমান্তিনী
গরু চোর
গরুচোর
সেদিন এক গরুচোরের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেল সবার, চোরটি নিজে থেকেই বলল—আমার নাম মজিদ। আমি একটা গরুচোর।
দলে নিয়োগ চলছিল। ইন্টার ডিস্ট্রিক বাস ডাকাতদলের সভাপতি জুম্মন খাঁ, অজ্ঞানপার্টি অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র সহ-সভাপতি, নিখিলবাংলা পকেটমার মহাসঙ্ঘের সেক্রেটারি বসা। এরাই দলের নিয়োগদাতা।
কিন্তু মজিদকে দেখে মোটেও গরুচোরের মতো লাগছিল না। গরুচোর হবে গরুচোরের মতো কিন্তু এরে সে রকম লাগছে না। এরে মকবুলের মতো লাগে।
মকবুল কে? মকবুল হলো মুরগি চোর। একসময় এই দলের হয়ে কাজ করত। এখন দল ভেঙে আলাদা দল করেছে। টেক্কা দিতে চায়।
অজ্ঞান স্পেশালিস্ট একাব্বর আলি সরু চোখে মজিদের দিকে তাকাল। তার ইচ্ছে করছে চোখেমুখে মলম ঘষে দিতে। একরাশ সন্দেহ নিয়ে বলল—তা মজিদ মিয়া, কয়টা গরু তুমি চুরি করছ?
মজিদ মাথা চুলকায়। ঘাড় চুলকায়। একটু লজ্জাও পায়। বলল—খুব বেশি না ওস্তাদ, আমি তো রেনডম গরু চুরি করি না। যখন কোরবানি আসে, গরুর হাটে ঘোরাঘুরি করে চান্সে চুরি করি। বছরে ওই একটাই সিজন আমার।
—তাই বল! একাব্বর হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সন্দেহ আমার ঠিকই ছিল—ভাবতে ভাবতে সবার দিকে তাকিয়ে একটু ফুলে ওঠে, গর্বে। আসলে এই ব্যাটাকে মুরগি চোরের মতো লাগছিল। বিশ্বাসঘাতক মকবুলের চেহারার লগে মিল আছে। মকবুলও ছিল বিরাট মুরগি চোর।
—তা এইখানে কি মনে করে?
মজিদ বলল—ওস্তাদ, আমারে দলে নেন। চুরিধারী দল থেকে না করলে পোষায় না। একলা একলা ভালো লাগে না। মামারা ধরলে ছাড়ানোর কেউ থাকে না কোর্টে চালান খাইয়া যাই।
মজিদের কথায় সিদ্ধান্তের জন্যে সেক্রেটারি তাকায় সহ-সভাপতির দিকে, সহ-সভাপতি তাকায় সভাপতির দিকে। সভাপতি কারো দিকে না তাকিয়ে নিজের ডানহাতের চার আঙুলে পরা আংটির দিকে তাকিয়ে রইল। দুর্লভ পাথর বসানো সব আংটি। কোনোটি হীরা। ইয়াকুত আর লাল জমরুদ পাথরের আংটি দুটি নাকি খুবই বিখ্যাত। সাদা চুনি নাকি পৃথিবীর কোথাও নেই। একটিই। তাও জুম্মনের হাতে, ভাবা যায়! এই আংটিগুলির বৈশিষ্ট্য হলো ডান হাতে পরতে হয়। কিন্তু জুম্মনের হাতে মোট আঙুল চারটি। একবার ডাকাতি করতে গিয়ে গৃহস্থের দায়ের কোপে একটি আঙুল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছিল। ফলে চার আঙুলেই আংটি পরতে হয়।
কাটা আঙুলের দিকে তাকিয়ে জুম্মন ডাকাত হতাশায় মাথা নাড়ে—মজিদ, গরুচোর মুরগি চোরের বিষয় না, আমরা এমন এক হাত সাফাইয়ের খোঁজ করছি, যে মুরগি নয়—মুরগির পিত্তথলি হাত চালিয়ে বাইরে আনতে পারবে, কিন্তু মুরগি টের পাবে না। পারবে?
ওস্তাদের কথায় খুব হতাশ হয়ে গেল গরুচোর মজিদ। চোখেমুখে পানি চলে এলো প্রায়। এত সুক্ষ্ম কাজ পারবে না সে। কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল—খুব ইচ্ছা ছিল আপনাদের সাথে কাজ করার। হলো না। বিদায় দেন ওস্তাদ।
বলে সবার সাথে হাত মিলিয়ে মজিদ চলে গেলে জুম্মন খাঁ নিজের আঙুলের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল—আমার আংটি, আমার আংটি!
…………
মকবুলের ডেরায় যখন মজিদ চারটি আংটি ছড়িয়ে দিল তখন খুব হাসাহাসি হলো, জুম্মন ওস্তাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেছে কল্পনা করে। হাত সাফাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়ে গেল মজিদ।
মকবুল কথা দিলে কথা রাখে।
গরুচোর
কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা
কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা
গ্রামের পাশে যে বিশাল বাদাম ক্ষেত আর ক্ষেতের পাশে যে ছোট নদী, সে নদীতে মাঝারি সব ঢেউ ওপার থেকে এপাড়ে আসে খড়কুটো মুখে নিয়ে। আর কত কিছু ভেসে আসে আর চলেও যায়—সারা দিনভর ছোটনেরা সেইসব দেখে পাড়ে বসে বসে।
ছোটনেরা মানে হলো—হাবিবুল, রতন, মোবারক, শেফালি বকুল এরা। কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা। তারা প্রতিদিন নদীতে আসে আর কাঁচা বাদাম খেতে খেতে লক্ষ করে নদীটাকে। নদীর ভেতরে কত কিছু। কাদাখোঁচা একটি দুটি। বালিয়া হাঁসের সাদা পাখনা উড়তে থাকে। আর ওপারের মেঘ যখন উড়তে উড়তে এপারে আসে তখন জলিল কাকার সময় হয় জোয়ালের গাই দুটাকে গোসল দেয়ার। গাই দুটার গোসল দেখতে দেখতে আর বাদাম খেতে খেতে দলের মধ্যে মোবারক নামে যে আছে, সে একটা প্রস্তাব দিল। প্রস্তাব দেয়ার আগে বিজ্ঞ বিজ্ঞ ভাব নিয়ে কয়েকটা জানাশোনা তথ্যও দিল। যেমন—এই নদীতে কিছুই ডোবে না।

বাকিরা মাথা নাড়ে—হুম।
গরু ডোবে না, খড় ডোবে না। নাও-লঞ্চ কিছুই ডোবে না। ভেলা ডোবে না।
সবাই মাথা নাড়ে। কাঁচা বাদাম খায়।
—চল আজকে একটা খেলা খেলি। মিনুরে ডুবাই দেই। দেখি ডোবে কি না?
ছোটনরা একজন আরেকজনের দিকে তাকায়। প্রস্তাবে জোর সমর্থন দেয় নুরু। প্রস্তাব সমর্থন নিয়ে নুরু কারো দিকে তাকায় না। নদীর পেটে জলের প্রবাহ দেখতে দেখতে তারা স্কুলঘর দেখে। দূরের আকাশছোঁয়া মিনার মসজিদ দেখে।
—মিনুও ডুবত না। এই নদীতে কিছুই ডোবে না–বলে সাহস দেয় নুরু। ততক্ষণে মিনুকে নিয়ে এসেছে মোবারক।
মিনু জল দেখে ভয় পায়। বলে—মিঁউ!
বিশাল নদী। বিশাল চর। মিনু ভয় পায়। ডাকাডাকি শুরু করে দেয়—মিঁউ মিঁউ।
মিনুকে কোলে নেয় হাবিবুল। হাবিবুল থেকে নেয় রতন। রতন থেকে নেয় শেফালি। শেফালি থেকে নেয় রাজন। রাজন থেকে নেয়া নুরু। নুরু থেকে কেউ নেয় না। কারণ নুরু কাউকে দেয় না। সে মিনুকে ছুড়ে দেয় নদীতে।
সবাই হাসে। মিনু সাঁতার কাটে। ঠিকমতো পারে না। নদীতে ঢেউ। তলিয়ে যায়। ছোট্ট মাথা। ডোবে ভাসে। সবাই হাসে–খুশিতে হাততালি দেয়।
দুই ঢেউয়ের চাপে পড়ে মিনু ডাকে—মিঁউ মিঁউ।
প্রাণপণ চেষ্টা করে মিনু কচি পা দিয়ে পাড়ে আসতে পারে না। দূরে সরে যায়। আবার আসে। পাড়ের কাছে আসেও। কিন্তু নুরুরা ঢিল ছোড়ে। হি হি করে হাসে। হাত তালি দেয়।
মিঁউ মিঁউ করতে করতে নদীর ভেতরে চলে যায় মিনু। ঢেউয়ের ভাঁজের ভেতরে চলে যায়। ডুবে যায়। পাড়ে বসে রাজন শিস দেয়।
…………
রাতের বেলায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে পুরো ব্যাপারটা আবার দেখে ছোটন। মিনু ডুবে যাচ্ছে। ভেসে উঠছে। চিৎকার করে ওঠে ছোটন। ঘামে নেয়ে ওঠে সে। কিন্তু তার ঘুম ভাঙে না। ঘুমের মধ্যেই ছোটন বোঝে ঘুম না ভাঙলে সে নদী থেকে আর মিনুকে উঠাতে পারবে না।
সকালবেলা তাড়াতাড়ি মিনু যে কাজটি করে তা হলো ছোটনের বাবা-মাকে নিয়ে নদীর পাড় চলে এলো। তারা দেখল—নদীর ভেতরে একটা লাল জামা ভাসছে ছোটনের।
২৪১৯
কালিয়াখোল গ্রামের ছোটরা
প্রেমালিঙ্গম
ঝুমকি
কত পথ পার হলাম ঝুমকি;
তবু মানুষ চেনা হলো না!
বারো প্যাচের নারী, চোখে জড়িচুমকির খেল্ দেখালো
অমলেশ সেই দেখে দেখে শেষে উন্মাদের খাতায় নাম লেখালো
পত্রিকার শেষ পাতায় ওকে নিয়ে কতো ফিচার হলো
তবুও অমলেশকে কেউ ভালোবাসলো না।
ঝুমকি পৃথীবির সবচে’ হিংস্র প্রাণী মানুষের
গায়ে বিপদের গন্ধ লেগে আছে;
ফাঁক পেলেই নষ্টামি করতে লেগে যায়
কেউ কেউ বলে সত্যিকারের ভালোবাসা নেই
বড় র্দূভাগা ওরা!
সত্যিকারের ভালোবাসাই দেখেনি চোখে; পাবে কোত্থেকে
প্রেমালিঙ্গম
সরদার ফারুকের ১০০ কবিতা
ভূমিকা-
আমার ৪টি কবিতার বই বিভিন্ন সময়ে কলকাতা এবং আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
বাংলাদেশের পাঠক বইগুলো হাতে পাননি বলেই সেখান থেকে ১০০টি কবিতা বাছাই করে এই প্রকাশনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
অনুপ্রাণন প্রকাশনের প্রাণপুরুষ শ্রদ্ধাভাজন আবু এম ইউসুফ ভাইয়ের সহৃদয় সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞ।
অনুজপ্রতিম তুহিন ভূঁইয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য অনেক ধন্যবাদ।
৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯
রূপনগর আবাসিক এলাকা
মিরপুর, ঢাকা।
সরদার ফারুকের ১০০ কবিতা
অন্যান্য
ফেসবুক রঙ্গ রসিকতা – গ্রন্থনা ও সম্পাদনা শফিক হাসান
ফেসবুক কি সময় নষ্ট করায়, দিয়ে যায় ক্লান্তি-হতাশা?
না; ফেসবুকের প্রাপ্তিও কম নয়। ইতিবাচক ব্যবহার করা গেলে। বিনোদনের দুনিয়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হয়ে উঠেছে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাঙালি জন্ম থেকে রসিক। কথাবার্তা থেকে যাপিত জীবনের কাজ-কর্মে রসবোধের পরিচয় মেলে। ফেসবুকও হয়ে উঠছে রসাধার।
কেউ কেউ স্ট্যাটাসে এমন সব কথা লেখেন। হা হা হা কিংবা খিলখিল করে হেসে উঠতে হয়। চেপে রাখার সুযোগ নেই। বাছাইকৃত মজাদার ও রসাত্মক ফেসবুক স্ট্যাটাস নিয়ে বইটি। খ্যাতিমান মানুষ থেকে সাধারণের মধ্যে যে রসবোধ প্রখর, প্রমাণ মিলবে এতে।
পাঠককে নিষ্কলুষ হাসি উপহার দেওয়ার প্রচেষ্টায় মেতেছেন শফিক হাসান। উদ্যোগ সার্থক নাকি অন্যকিছু সেই চিত্রই ফুটে উঠেছে বইয়ের পাতায় পাতায়।
Facebook Rongo Rosikota - Collection & edited by Shafique Hasan
কুনাফার শহরে – ক্ষমা মাহমুদ
ভ্রমণকাহিনি কেবল কোনো জায়গার প্রকৃতি বা রূপ বর্ণনাই নয়, তার সঙ্গে অনুপান হিসেবে থাকতে হয় জায়গাটার ইতিহাস-ঐতিহ্য, মানুষ এবং তাদের জীবনযাপনের সুলুক-সন্ধানও। তবে তথ্য বা ইতিহাসের অনুপাত কতখানি হবে, তারও রয়েছে কিছু অলিখিত হিসাব। তথ্য-উপাত্ত এবং সাহিত্যরসের ভারসাম্য রক্ষা করে একটা উপাদেয় ভ্রমণবৃত্তান্ত উপস্থাপন করার ক্ষমতা একজন কুশলী ভ্রমণলেখকের বিরল গুণ। এই বইতে এসব উপাদান ও রসে জারিত সাতটি ভ্রমণগল্প পাঠককে নিয়ে যাবে জর্ডানের ইতিহাসের অলিগলিতে যেখানে থমকে আছে হাজার বছর আগের সময়, যার পরতে পরতে পাওয়া যাবে নানান জানা-অজানা তথ্য।
গ্রেকো-রোমান সময়ে জর্ডানের রাজধানী আম্মানের নাম ছিল ফিলাডেলফিয়া, আরব দেশ হলেও জর্ডানে যে একসময় গ্রিক রোমানদের জবরদস্ত উপস্থিতি ছিল-সেসব নিদর্শনের সুস্বাদু বর্ণনা ও ইতিহাস পাওয়া যাবে এই বইতে। নরম হলুদ গমের মতো মিঠে রোদমাখা আরাম পাওয়া যাবে ওয়াদিরাম মরুভূমিতে যাযাবর বেদুইনদের ঘরবাড়ি আর জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বর্ণনায়। আবার পাওয়া যাবে একই মরুভূমিতে তাঁবুর ভেতর রাতের তারা দেখে রাত কাটানোর বিরল অভিজ্ঞতাও। প্রাচীন রূপকথার মতো অবিশ্বাস্য সুন্দর পাথুরে নগরী পেত্রার ভেতর ফারাও রাজাদের ধন ভান্ডারের দরজাও যেন খুলে যাবে বর্ণনার মুনশীয়ানায়। জর্ডানের মৃত সাগরের জীবন্ত বর্ণনার সঙ্গে এই সাগরটি সম্পর্কে বহু মিথ ভেঙে দিয়ে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি বর্তমান যুগের বাণিজ্য-আগ্রাসনে এই বিচিত্র সাগর যে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে লেখকের উদ্বেগের আভাসও পাওয়া যাবে এই বইতে।
Kunafar Shahore - Khama Mahmud
দেখি বাংলার মুখ – শফিক হাসান
শফিক হাসানের দেখা বাংলার মুখ আদতে কেমন!
‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া’
তারপরের কথা—‘একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু’।
মনে এই খেদ যেন না থাকে, শফিক হাসান বেরিয়ে পড়েছেন বাংলাদেশের নানা জায়গা প্রাণভরে দেখতে। তার বর্ণনা রম্য, সহাস্য আনন্দময় ও প্রাঞ্জল। নানা সব জায়গার ভেতরে—লালনের স্মৃতিভরা স্থান, কেওক্রাডং চূড়া, মুজিবনগর, কক্সবাজার, চট্টগ্রামের নানা জায়গা, সমুদ্র ও পর্বত, রেলযাত্রায় তূর্ণা নিশিথায় নিশিযাপন এবং জলজোছনায় ভেসে যাওয়া হাতিরঝিল—এমনি মায়াময়, সুরভিময় নানা স্থানে। আমরা যখন ফট করে বাইরে ঘুরতে যাই কখনো কি ভাবি দেশের কতটুকু দেখেছি।
না, শফিক হাসান তেমন কোনো খেদ করবেন না যেদিন বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়বেন। ‘দেখি বাংলার মুখ’ এমনই একটি গ্রন্থ। সবকিছু দেখার আগে নিজেদের দেখো। অপূর্ব। সুন্দর ঝরঝরে গদ্যে দেখার সেইসব বর্ণনা আমাদের দেশটাকে নতুন করে চেনাবে। আমি এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।
সালেহা চৌধুরী
ঢাকা
মার্চ, ২০২৪
Dekhi Banglar Mukh by Shafique Hasan
সুপ্রিয় দিনলিপি ( দ্বিতীয় খণ্ড)
ভূমিকা
মূলত: ‘সুপ্রিয় দিনলিপি’ শিরোনামে আমার এই লেখাগুলো যে শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, লেখাগুলো যে আসলেই মান-সম্পন্ন, পরিশীলিত এবং এতে যে সামগ্রিকভাবে একটি স্পষ্ট বক্তব্য বা ম্যাসেজ বিদ্যমান থাকে এবং তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও প্রকাশিতও হচ্ছে- এই সামগ্রিক ব্যাপারটি আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি বহু বছর পরে, ১৯৯৮ সালের দিকে যখন ‘দৈনিক ভোরের কাগজ’ এ আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয়। তখন আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর বিবিএ (অনার্স) এর শিক্ষার্থী। এরপর জীবনের বিভিন্ন সময়ে সাহিত্য, ছোট-গল্প, বিভিন্ন ন্যাশনাল ইস্যু, উপন্যাসের সমালোচনা, বঙ্গবন্ধুর জীবনী, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন বিষয়াবলীর ওপর আমার আর্টিক্যাল ও কলামগুলো একে একে দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক ভোরের কাগজ, দৈনিক আজাদী ইত্যাদি জাতীয় দৈনিকগুলোতে প্রকাশিত হতে থাকে। দ্যাট মীনস্ সিরিয়াসলি কাউন্ট করলে আমার লেখালেখির বয়স হচ্ছে বিশ (২০) বছর। কিন্তু যেহেতু আমি প্রফেশনাল রাইটার নই, তাই আমার লেখাগুলো প্রকাশিত হয় অনিয়মিতভাবে এবং সংখ্যায় খুবই কম। ‘সুপ্রিয় দিনলিপি’ শিরোনামে এখনো আমি ক্লান্তিহীনভাবে লিখে যাচ্ছি। এই পর্যন্ত আমার সেইসব লেখা সর্বমোট ১৯টি ডায়রীতে এসে দাঁড়িয়েছে। সেখান থেকে বাছাইকৃত কিছু লেখার ‘পরিবর্ধন -পরিমার্জিত’ রূপ নিয়েই রচিত ‘সুপ্রিয় দিনলিপি (দ্বিতীয় খণ্ড)’ পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করার নিমিত্তে। গ্রন্থটিকে রূপক অর্থে মূলতঃ ‘একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ’ও বলা যায়। এই গ্রন্থটিতে প্রধানত যে সময়কালের ঘটনাবলী বিশ্লেষনাত্মকভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেই সময়কাল হচ্ছে- ২০০১ সাল থেকে ২০০৬ সাল। অদূর ভবিষ্যতে ক্রমান্বয়ে ‘সুপ্রিয় দিনলিপি’ এর- তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ডে পরবর্তী সময়কালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণাত্মকভাবে তুলে ধরা হবে এবং একটা পর্যায়ে এর ইংলিশ ভার্সনও বের করা হবে- এইরকম একটি প্লান আমার রয়েছে।
আমি মনে করি,
“সময়ের সাথে সাথে নিজের মন ও মেধাকে আপডেটেড রেখে ধর্মীয় কুসংস্কার, বিজাতীয় সংস্কৃতির আধিপত্য ও দৌরাত্ম্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা, পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মেধার অবমূল্যায়ন, শিক্ষা-ব্যবস্থার ভগ্নদশা, শিক্ষকদের অবমূল্যায়নসহ সামাজিক আরও নানা অসঙ্গতি, দুর্নীতি পরিহার করে বাংলাদেশের যে নিজস্ব একটি আদর্শ, ঐতিহ্য, ইতিহাস, কৃষ্টি-কালচার, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক মূল্যবোধ রয়েছে- সামগ্রিকভাবে তার অনুশীলন করা- বাঙ্গালী জাতি হিসেবে আমাদের সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ১৯৭১ সালে সবাই সময়ের প্রয়োজনে যুদ্ধ করেছিল, তখন যুদ্ধ করে দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে ‘স্বাধীন’ করাই ছিলো তখনকার সময়ের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। আর এখন আকাশ-সংস্কৃতির এই আগ্রাসনের যুগে অর্থাৎ এই সময়ের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন হচ্ছেÑ ‘আলোকিত এবং একই সঙ্গে মানবিক, দেশপ্রেমিক, নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন , অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, আধুনিক মানুষ ও চাই, যাতে করে একটি উন্নত ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যেÑ আমরা বাংলাদেশের সকল মানুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারি ঠিক সেই মুক্তিযুদ্ধের মতো।
অর্থাৎ বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি আত্মনির্ভরশীল, সংস্কারমুক্ত, স্বশিক্ষিত, মেধাবী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরতে হলে- আমাদের সকলকে আরেকটি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং যেখানে আমাদের মূল অস্ত্র হবেÑ আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা ও অন্যান্য সকল জাতীয় অর্জন এবং একই সঙ্গে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের বহিঃপ্রকাশ! ‘আলোকিত মানুষ চাই এবং একই সঙ্গে মানবিক, দেশপ্রেমিক, নৈতিকমূল্যবোধসম্পন্ন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, আধুনিক মানুষও চাই’- মূলত এটাই হওয়া উচিত আধুনিক বাংলাদেশ এর শ্লোগান’।
রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘পৃথিবীর উপকার করতে চাইলেও করা যায় না, তার চেয়ে বরং আমরা যা করতে পারি তাই যদি করি তাহলে আপনা-আপনি পৃথিবীর উপকার হয়ে যায়’।
মূলত: পাঠকের ভালো লাগা এবং ভালোবাসাই হচ্ছে লেখকের প্রত্যাশা পূরণ। আশা করি, আপনারা কখনো আমাকে এবং আমার লেখাকে সেই ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করবেন না। আমি মূলত প্রফেশনাল রাইটার নই। আমার মূল পেশা ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করা’ আর নেশাÑ ‘লেখালেখি করা’। ‘পেশা’য় জড়িত না থাকলে আমার এ পৃথিবীতে জীবন-ধারণ ও অস্তিত্ব রক্ষাই দুরূহ হয়ে উঠবে কিন্তু ‘নেশা’টা আমার মাঝে-মধ্যে করলেও চলবে। ‘শিক্ষকতা’ পেশায় ব্যস্ত থাকার কারণে, এই গ্রন্থটির প্রতি হয়তবা পরিপূর্ণ মনোনিবেশ ঘটাতে পারিনি। ‘সুপ্রিয় দিনলিপি (প্রথম খণ্ড) অথবা সুপ্রিয় দিনলিপি (দ্বিতীয় খণ্ড)’ এর কোথাও যদি পাঠকেরা অতৃপ্তি কিংবা অসম্পূর্ণ ফিল করেন, তাহলে তাদের কাছে অনুরোধ- ‘আপনারা রেগুলারলি ‘সুপ্রিয় দিনলিপি’-এর পরবর্তী খণ্ডগুলো সংগ্রহ করবেন’। আশা করি, তাহলে আর কোনো অতৃপ্তিবোধ থাকবে না। উল্লেখ্য, সুপ্রিয় দিনলিপি (দ্বিতীয় খণ্ড) -এর পাঠকগণ ‘অনুপ্রাণন প্রকাশন’ থেকেই ‘সুপ্রিয় দিনলিপি (প্রথম খণ্ড)’-বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন।
‘সুপ্রিয় দিনলিপি’ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে বাংলাদেশের যে দু’জন স্বনামধন্য সাংবাদিক সবসময় সহযোগীতা ও উৎসাহ যুগিয়েছেন, তারা হচ্ছেনÑ ১. সাংবাদিক ‘সালিম সামাদ’ (বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য সাংবাদিক) যিনি ‘দি ডেইলী আওয়ার টাইমস্’ সহ আরও বেশ কয়েকটি সংবাদপত্রে এ কাজ করছেন এবং তিনি ২০০৫ সালে প্রেসটিজিয়াস ঐবষষসধহ-ঐধসসবঃঃ অধিৎফ অর্জন করেন এবং একসময় ‘ইন্ডিয়া টু ডে’, ‘বাংলাদেশ অবজাভার’, ‘বিবিসি’সহ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে ঈড়ৎৎবংঢ়ড়হফবহঃ ধহফ জবঢ়ড়ৎঃবৎ হিসেবে কাজ করেছেন এবং ২. সাংবাদিক ‘রাশেদ রউফ’ যিনি বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় দৈনিক ‘দৈনিক আজাদী’র সহযোগী-সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে কর্মরত। তিনি একই সঙ্গে বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য শিশু-সাহিত্যিক এবং কবি। তিনি ২০১৬ সালে ‘বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করেন।
এ গ্রন্থটির প্রচ্ছদ নির্বাচন করেছেনÑ সাংবাদিক, কবি ও শিশু সাহিত্যিক ‘রাশেদ রউফ’ এবং গ্রন্থটি প্রকাশনা করেছেন ‘অনুপ্রাণন প্রকাশন’। হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞচিত্তে সাংবাদিক ‘সালিম সামাদ’, ‘রাশেদ রউফ’ এবং ‘অনুপ্রাণন প্রকাশন’ এর কর্ণধারসহ সকল কলাকুশলীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
ফারহানা আকতার
মিরপুর, ঢাকা, বাংলাদেশ
১৫ জানুয়ারি ২০২০
Suprio Dinlipi, Part-2
মুক্তি-সংগ্রামের গান
লেখকের কিছু কথা–
১৯০৬ সাল থেকে রচিত মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণাদায়ী ক্ষুরধার গানগুলো নিয়ে কাজ করার তীব্র অনুভবে তাড়িত হই। গান নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা না-করার অভাব থেকে এ গবেষণার জন্ম। সুযোগ আসে ২০০৯ সালে। তা অবশ্য কিছু দূর এগোনোর পর শেষও হয়ে যায়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে আবার কাজটি শুরু হয় সরকারি অর্থায়নে। তখন নতুন করে সাজাই ফেলোশিপ গবেষণার সূচিপত্র।
আগে চেয়েছিলাম সময়ক্রমে গবেষণা কাজটা করতে; পরে ‘মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রেরণা-সৃষ্টিতে দেশাত্মবোধক গানের ভূমিকা (১৯৪৭-৭১)’ গবেষণার অধ্যায় বিভাজন করি—
ভূমিকা, দেশাত্মবোধক গানের পটভূমি, ১৯৪৭-৫২ সনের ভাষা আন্দোলন পর্বের গান, ১৯৬৯-৭০ সনের গণ-অভ্যুত্থান পর্বের গান এবং ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ পর্বের গান।
তবে শেষের পর্বটিতে তিনটি সেমি-পর্ব যুক্ত হয়—প্রেরণামূলক বঙ্গবন্ধুর গান, সংগ্রামে-সংগীতে নারীর অবদান এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান।
গ্রন্থটিতে ভাষা সৈনিক আবদুল মতিন এবং নজরুল স্বরলিপিকার সুধীন দাস এবং বিশিষ্ট গণ সংগীতশিল্পী শুভেন্দু মাইতি (যিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অর্থ সংগ্রাহক ছিলেন)—তিন বিশিষ্ট জনের সাক্ষাৎকার সংযোজিত হয়েছে। প্রায় ৯০০টি দেশপ্রেরণামূলক গানের তালিকা দেয়া হয়েছে।
গবেষণার দীর্ঘ পথে অনেক বাঁধার সম্মুখীন হই। তবে ধৈর্য ধারণ করে সবটা সহ্য করেছি; গবেষণা কর্মের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। পরম করুণাময়ের অপার কৃপায় কাজটি শেষ করতে পেরেছি। তিনি সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন; সে প্রমাণ প্রতি মুহূর্তেই পেয়েছি। বাকিটা বিবেচনার ভার সম্মানিত পাঠকদের।
ফেলোশিপ গবেষণাটির প্রকল্প পরিচালক হিসেবে সার্বিক দায়িত্বে ছিলাম আমি।
যাদের আন্তরিকতা, সহযোগিতা পেয়েছি, তারা হলেন—
শ্রী গোবিন্দলাল দাস, শ্রী করুণাময় অধিকারী, জনাব ড. মূহ: আব্দুর রহীম খান, লিপিকা ভদ্র, সঞ্জয় কুমার বণিক, মল্লিকা দাস, ড. সাইম রানা, ড. সেলুবাসিত, ড. মোহাম্মদ গিয়াসউদ্দিন (গিয়াস শামীম), ড. রঘুনাথ ভট্টাচার্য, আবদুল মতিন, সুধীন দাস, শুভেন্দু মাইতি, মোবারক হোসেন খান, সেলিম রেজা প্রমুখ সুহৃদগণ। সবাইকে কৃতজ্ঞ-চিত্তে স¥রণ করছি।
সময়ে-অসময়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যাদের, তারা হলেন আমার পূজনীয় শিক্ষক—ড. সাঈদ-উর রহমান এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক।
গবেষণা কাজটির মূল্যায়ন করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক। তার আশীর্বাদকে ভক্তি জানাই।
‘মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম’-এ প্রেরণাদায়ী গানগুলোর যাদুমন্ত্রে যুদ্ধ জয়ের নেশায় বীর বাঙালি দুর্বার গতিতে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা।
সেই গানগুলোর পটভূমি এবং গানগুলো সম্পর্কে সকলে জানতে পারবেন যার সহযোগিতা, সহমর্মিতায় তিনি—অনুপ্রাণন প্রকাশনের সত্ত্বাধিকারী আবু এম ইউসুফ ভাই। এই ফেলোশিপ গবেষণা ও সমীক্ষা ধর্মীগ্রন্থটি অনুমোদন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেবার জন্য তার প্রতি অপরিসীম আন্তরিকতা প্রকাশ করছি। ২০২০ সালের বইমেলার বই-প্রকাশনার সীমাহীন ব্যস্ত সময়ের মধ্যেও গ্রন্থটির নামকরণ করে তিনি কৃতজ্ঞাপাশেবদ্ধ করেছেন।
ড. শিল্পী ভদ্র
ঢাকা।
মুক্তি-সংগ্রামের গান